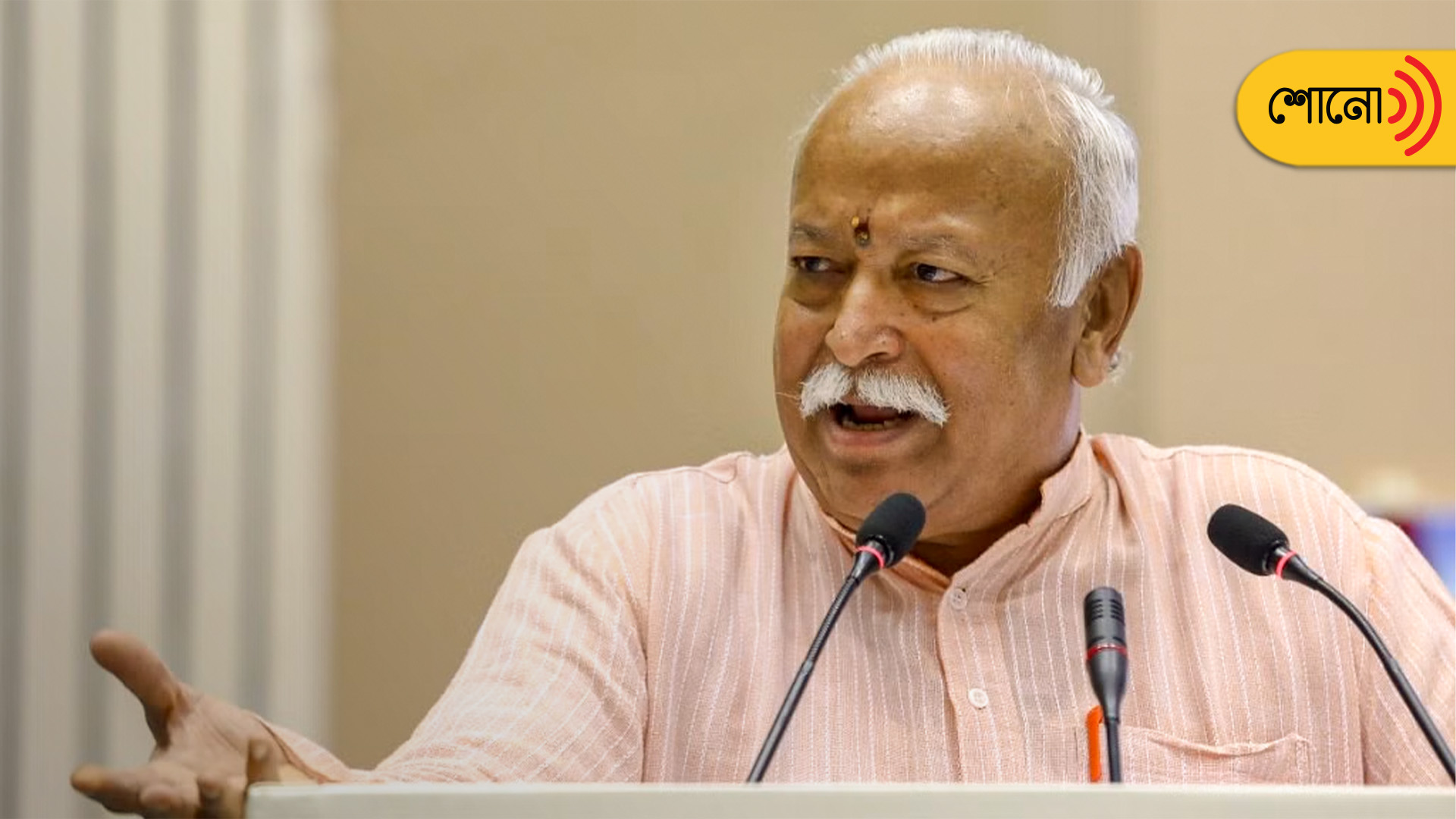পয়লা-Podcast: বছরভর অন্যকে নকল করে পয়লা বৈশাখে ‘পোশাকি’ হয়ে ওঠে বাঙালি । শুভঙ্কর দাস
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: April 14, 2025 8:29 pm
- Updated: April 14, 2025 9:03 pm

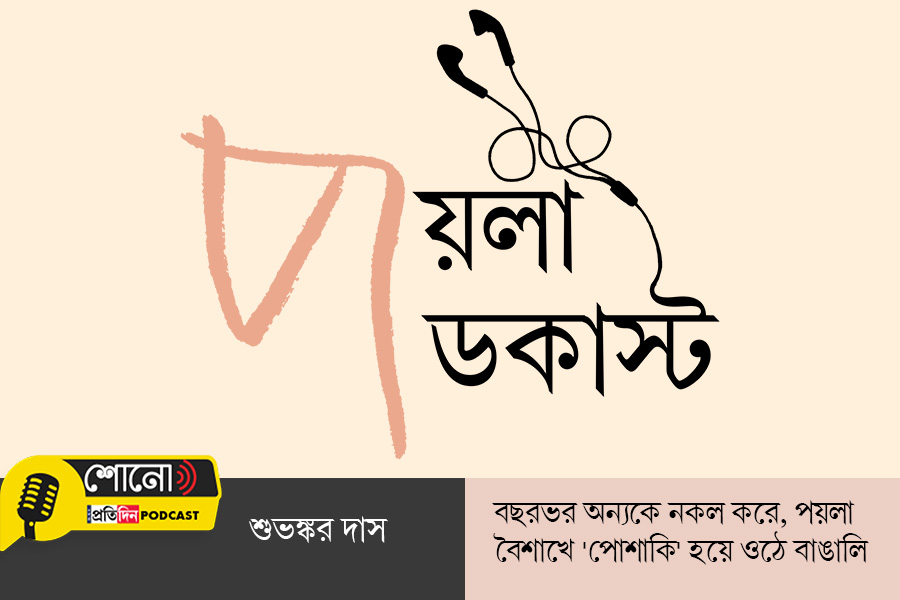
বাঙালির পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখের বাঙালি। ঠিক আগের মতোই আছে! নাকি পয়লা বৈশাখ নেহাত পোশাকি উদযাপনে এসে ঠেকেছে? তা নিয়েই নিজের ভাবনা জানালেন, শুভঙ্কর দাস।
পড়ে শোনালেন: শঙ্খ বিশ্বাস। গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক।
রাঙাপিসি, ফুলকাকুরা আর নেই। সেই উঠোন, তুলসী মঞ্চ, বাড়ির রোয়াক, শীতলপাটিতে মুড়ে যাওয়া ভালবাসার বারান্দা কেবলই অতীতের শিলালিপি। তালপাতার পাখায় স্নিগ্ধ বাতাসে ঠাকুরমার স্নেহপরশ আর নেই। যে রূপকথার গল্পগুলো শুনতে গিয়ে শিশুরা নিজের কল্পনার রাজত্বকে আরও বিস্তার করত, তা আজ কেবলই অতীতের ছায়া হয়ে থেকে গিয়েছে।
তার জায়গায় এসেছে রিল-সংস্কৃতি। গো-বলয়ের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি। আজ পটচিত্রের গান কেউ প্রতিটি বাড়িতে শোনাতে আসে না। বাঙালি মেলা আর মিলনক্ষেত্র নেই, তা বাজারে পরিণত হয়েছে। মেলায় হারিয়ে গিয়েছে পুতুল নাচের চরিত্রগুলো। যাত্রাপালার জায়গায় এসেছে ডিজে পার্টি। ড্রোন ওড়ানোর নেশায় আজ বাঙালির ছাদে নেই পেটকাটি, চাঁদিয়ালের দাপট। রাত জেগে ঘুড়ির সুতোতে মাঞ্জা দেওয়া আর রোমাঞ্চ দেয় না বাঙালিকে। শুধু গান গেয়ে ভাদুকে পুজো দেওয়ার লোকজ অভ্যাস বিদায় নিতে শুরু করেছে রাঢ় বঙ্গ থেকে। বাসন্তী পুজোর সময় চতুর্দোলা সাজিয়ে নবদ্বীপের শিবের মুখোশ নিয়ে বৃত্তি তোলা বা নিজ ভাবনায় ঝুলন সাজানোতে বড্ড অনীহা তার। বাঙালির ফেলে আসা আটপৌরে জীবনশৈলীতে বিকেলে মুড়ি খাওয়া, শীতে গায়ে কাঁথা জড়ানো, ডাল বেটে বড়ি তৈরি করা, গরমে আখের গুড়, তালমিছরি খাওয়ার মতো অভ্যাসগুলো মলিন হতে শুরু করেছে। মোহনভোগ, মাখা সন্দেশের মতন সরল গ্রাম্য মিষ্টি তার মুখে রোচে না। সে ছুটে চলেছে বিজ্ঞাপননির্ভর আধুনিকতার দিকে। সহজ স্বাভাবিক আটপৌরে জীবন তার আর ভালো লাগে না। সে ক্রমাগত নিজের সংস্কৃতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজ ঐতিহ্য ও ভাষার প্রতি তার আর আস্থা নেই। সে সবকিছুকে টাকার দাঁড়িপাল্লায় মেপে চলেছে। তার বুদ্ধিমত্তা নিছক দেখনদারীতে এসে ঠেকেছে। আত্মচিন্তন, আত্মমন্থন থেকে সে দূরে সরে গিয়েছে।
ইন্টারনেট এলেও তার মন ফেলে আসা বাঙালিয়ানার বিশ্বমানববোধ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেই পাঁচ ও ছয়ের দশকে যখন বিশ্বায়নের গালভরা বিজ্ঞাপন ছিল না, তখনও বাঙালি পিট সিগারকে শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছে। পল রবসনের কণ্ঠে খুঁজেছে মুক্তির স্বাদ। হেমাঙ্গ, দেবব্রত বিশ্বাসের গানে বাঙালির গণচেতনা ঐক্যের সঙ্গীত গেয়েছে। ডি সিকার ‘বাই সাইকেল থিবস’, ‘সু সাইন’-এ সে প্রতিবাদের ভাষ্যকে জেনেছে। ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সে বিশ্ব চলচ্চিত্রের নির্যাসকে নিজ ভাবনায় স্থাপন করতে চেয়েছিল। সে তার বিশ্বভাবনাকে নিজের ভাষায় ভেবেছে। হিরোশিমা-নাগাসাকি, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কিউবা সংকট তাকে নাড়িয়ে দিয়ে যেত। এমন নয় যে সেই সময় বাঙালি সুখে ছিল। তখন অভাব ছিল আরও তীব্র। কিন্তু তার মনের জানালায় বসন্তের বাতাস খেলা করে যেত। আজ আমাজন পুড়ে যায়, ইউক্রেন কাঁদে তবুও বাঙালির মন স্থবির হয়ে থাকে। আজকের সময়ে বাঙালিয়ানার বিশ্বচেতনা বোধ থেকে সে সরে এসে ‘আমার ছেলে আমেরিকায় থাকে আর রাজারহাটে ফ্ল্যাট কিনেছে’ বলে অহং বোধে ভোগে।
বর্তমানে বাঙালির মনে নিজ সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতাবোধ তৈরি হয়েছে। আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অচল আর হিন্দি বলয়েরটা চটকদার, মজাদার, এমন ধারণা পোষণ করছে সে। সেই কারণে তার খাদ্যাভাস থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র নির্মাণ, ধর্মবোধ, সমাজকে দেখার দৃষ্টিকোণে গোবলয়ের চাপ স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। অথচ তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সেটা সে ভুলে গেছে। তাই তো চন্দ্রকেতুগড়, পান্ডু রাজার ঢিবি তাকে টানে না। অথচ একটা সময় ছিল যখন নিজের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এই জাতির মধ্যেই জন্ম নিয়েছিলেন গুরুসদয় দত্ত। প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে যিনি গড়ে তুলেছিলেন বাংলার প্রথম লোকসংস্কৃতির সংগ্রহশালা। বাঙালির সামান্যতম বাঙালিয়ানা আজ সামাজিক মাধ্যমে স্ট্যাটাসের পোস্টে এসে ঠেকেছে। বছরে একদিন পাঞ্জাবি পরে হলুদ ট্যাক্সি বা কলকাতার হাতে-টানা রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে, সেটা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে নিজেকে বাঙালি হিসেবে প্রমাণ করার লোকদেখানো প্রচেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে যে ভাষা রক্ষার জন্য তার পূর্বপুরুষ প্রাণ দিল, আজ সেই ভাষাতেই কথা বলতে লজ্জা বোধ করে বাঙালি। এর জন্যে ভিনরাজ্যের মানুষকে দায়ী করে লাভ নেই। বর্তমানে বাঙালি নিজেই নিজের ভাষার প্রতি ক্রমাগত অনীহা দেখিয়ে চলেছে। তার ভাবনার ব্যাপ্তি কমে গিয়েছে। বিশ্বচেতন ও নিজের সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসায় বিভোর থাকা বাঙালি আজ শুধু ইংরেজি, বা হিন্দি ও বাংলা মেশানো ভাঙাচোরা ইংরেজি বলতে পারাতেই নিজের সার্থকতা খুঁজে পায়। তাই সরকারি বাংলামাধ্যম স্কুলগুলোতে সে নিজে চাকরি পেতে চায়, কিন্তু সন্তানদের পড়ায় বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমে।
বছরের প্রায় প্রতিটিদিন যে জাতি অন্যকে নকল করে যায়, সে নিজে বছরের এই একটা দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে পোশাকি বাঙালি হয়ে ওঠে। নিছকই সে আনুষ্ঠানিক বাঙালি থেকে যায়।