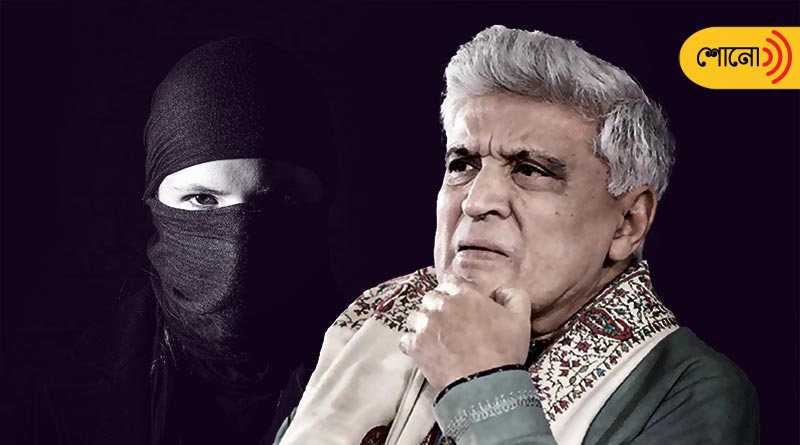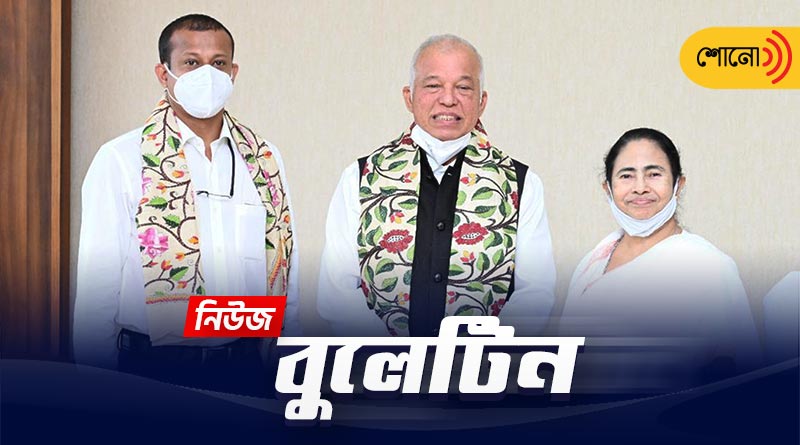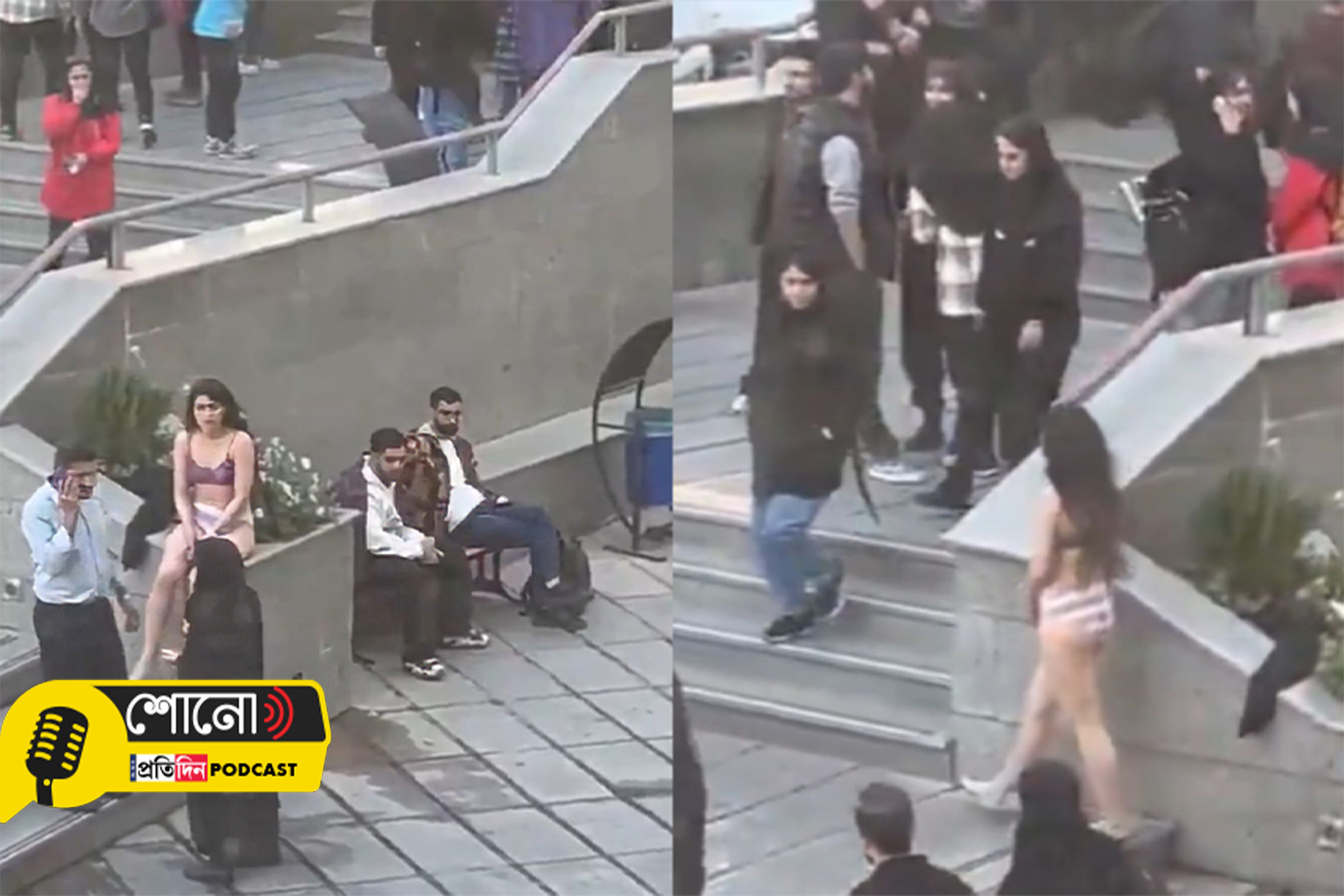পয়লা-Podcast: পান্তা-ইলিশের বোশেখ একমাত্র ঐতিহ্য নয়। দিব্যেন্দু ঘোষ
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: April 14, 2025 5:12 pm
- Updated: April 14, 2025 9:22 pm

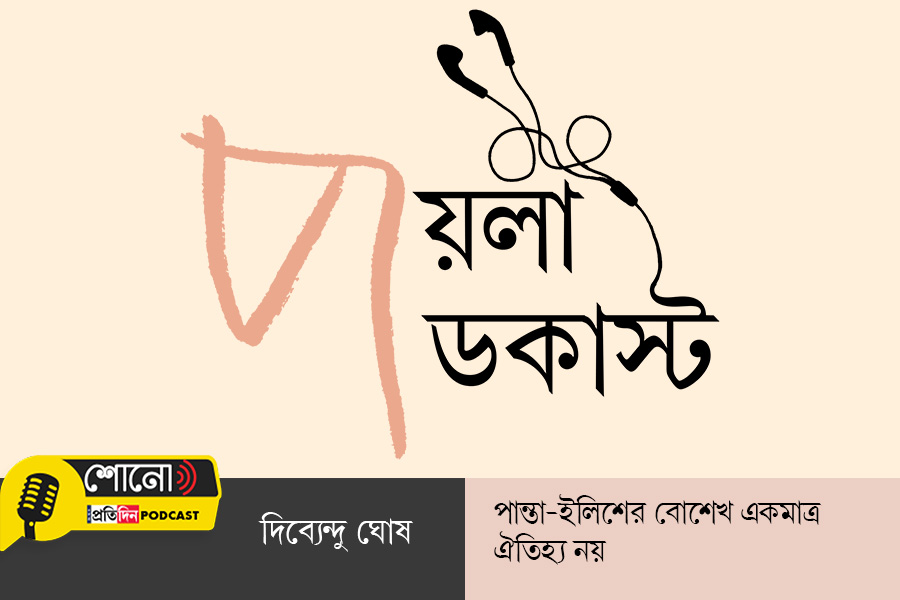
বাঙালির পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখের বাঙালি। ঠিক আগের মতোই আছে! নাকি পয়লা বৈশাখ নেহাত পোশাকি উদযাপনে এসে ঠেকেছে? তা নিয়েই নিজের ভাবনা জানালেন, দিব্যেন্দু ঘোষ।
পড়ে শোনালেন: শঙ্খ বিশ্বাস। গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক।
মুঠোফোনে ধাঁই করে মেসেজ, ‘হ্যাপি নতুন ইয়ার’। প্রথমা বোশেখে ভেতো বাঙালি বিরিয়ানি-চাঁপ সাঁটিয়ে দিনেদুপুরে মেসেঞ্জারে ‘হাই’ তুলছে, কিন্তু ঘুমোচ্ছে না। বরং মেসেজের রকমসকম দেখে ছিটকে ছ’ হয়ে পোশনো তুলছে, ‘ইয়ার, মসকরা হচ্ছে! এটা বাংলা নতুন বছরের শুরুয়াৎ, ইয়ার। মায়ের দেওয়া মোটা আঙুলকে শিক্ষা দে, বাংলা লেখ। হালকা নীল ইনল্যান্ড লেটার গন, হলুদ পোস্টকার্ডও কালের গর্ভে, চিঠি না লিখিস, বাংলা টাইপটা অন্তত কর হতচ্ছাড়া, শুভ নববর্ষ।’
সে গুড়ে বালি!
যা কিছু খাওয়ার সাধ হয়, খেয়ে নেওয়া যাক প্রথমা বৈশাখে। গরম ভাতে জল ঢেলে পান্তা, মচমচে ইলশে ভাজা। নতুন কেনা মাটির বাসনে চুমুক দিয়ে চুকচুক করে পান্তার জল, আর উগরে দেওযা তৃপ্তির ঢেকুর- ‘আহ! বড্ড বাঙালি হলুম!’
তবে, পয়লা সকালে পান্তা-ইলিশ, এ যে গালভরা বুলি, এ ‘পোশাকি ঐতিহ্য’ বাঙালির নয়। এসব বুলিবাজেরাও বাঙালিদের কেউ নয়। আমাদের ছিল ডাঁটাশাক বুনোকচু কলমিলতা, আমাদের ছিল আলুভর্তা কুমড়ো ভাজা মাসকলাইয়ের ডাল, আমাদের ছিল খলসে ট্যাংরা চিংড়ি আর পুঁটিমাছের ঝোল, আমাদের ছিল খাল-বিল-পুকুর-ডোবার সহজ জীবন। আমাদের ছিল চৈত্রসংক্রান্তি, গ্রামে গ্রামে মেলা, পাগলা ষাঁড়ের কাছি ছেঁড়া, আমাদের ছিল হালখাতা। ধান্দাবাজ, পুঁজিবাজ, অর্থখেকো আড়ৎদার আর মিডিয়ার তৈরি কৃত্রিম ‘পান্তা ইলিশের বোশেখ’ ছাড়ো। তোমরা আবহমান বাংলার কেউ নও। কোনওদিন দেখোনি বাংলার গ্রাম, বাংলার ঘরে যাপন করোনি একটি নিশুতি। সেই তোমাদের মুখে যখন শুনি পান্তা-ইলিশ হইল বাংলার ঐতিহ্য, তখন চিত্ত চমকে চ’।
তখন বোশেখি বাঙালি সন্ধে হলেই হালখাতার আমেজে গা সেঁকে নিত। জমানা ডিজিটাল, তাই বোশেখি বাঙালির সেই সব হালখাতা গোডাউনে পড়ে পড়ে রংচটা বা পুরনো খাতা-কাগজ বিক্রেতার ঘরে ডাঁই। দোকানে দোকানে সেই দেদার ভিড় নেই, হাতে লাড্ডু, গজার প্যাকেট নেই, পেলাসটিকের গেলাসে ঠান্ডা পানীয় বুজকুড়ি কাটে না। এখন অধিকাংশ দোকানির ভরসা ডিজিটাল ইনভিটেশন! পাড়ার মুদিখানাই হোক অথবা জামাকাপড়ের দোকান, সকলেই নিমন্ত্রণ সারে হোয়াটসঅ্যাপে।
এখন বাঙালি পয়লায় রেস্তরাঁয় চাইনিজ সাঁটায়। মোদ্দা কথা, পহেলা বোশেখে বাঙালিয়ানার পালে যে-হাওয়া লাগত জোরসে, চুপসে চোদ্দ হয়ে যাওয়া ভাষা-সংস্কৃতিতে সে-হাওয়া আজ ফিকেতর। আসলে শুরুতে ‘বৈশাখ’ বছরের প্রথম মাস ছিল না, শুরুর মাস ছিল অগ্রহায়ণ। পরবর্তীকালে অগ্রহায়ণকে হটিয়ে এ স্থান দখল করে নিল বৈশাখ। অর্থাৎ ঐতিহ্যের হেরফের ঘটল। আসলে চিরন্তন বলে যে কিছু নেই! সুতরাং ‘হাজার বছরের সংস্কৃতি’ বলাটা আতিশয্য ছাড়া আর কী!
নববর্ষের সেই মেলা ফুরিয়ে গেছে, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে নাগরদোলা ঘোরে না, পুতুলনাচ তো কবেই নাচতে নাচতে পগার পার। বাঙালির মনের ভেতর আজ শৈশব উঁকিঝুঁকি দেয় না, অসংখ্য এলোমেলো স্মৃতিরা আজ ঝাপসা। চিলেকোঠার চুমু-বাহিত শরীরে লেপ্টে নেই ঐতিহ্যের লেশ! নাগরিক জীবনে আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির ঘেরাটোপে পড়ে থাকে পোশাকি বাঙালি। নববর্ষকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলায় প্রচলিত সংস্কারকে নগর কিংবা উপ-নগরবাসী কতিপয় ‘শিক্ষিত’ ব্যক্তি নিছক ‘কুসংস্কার’ বলে উড়িয়ে দিতে চায়, তারা স্বঘোষিত উন্মূল। তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেম ঠাহর করতে পারে না, কিন্তু ঠিকই মহাআড়ম্বরে উদযাপন করে ভ্যালেন্টাইনস্ ডে।
বিশাল বাংলার সংস্কৃতিকে খাটো করে দেখার উপযোগী শব্দ ‘ফোকলোর’ এখনও বহাল। হালে আরও একটি ইংরেজি অভিধা শোনা যায়, সাবঅল্টার্ন বা নিম্নবর্গ। এসব আধিপত্যবাদীমূলক শব্দগুলো দিয়ে এ ইঙ্গিতই করা হয় যে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিটাই হচ্ছে এ দেশের মূলধারার সংস্কৃতি আর বিশাল বাংলার সংস্কৃতি হচ্ছে পদানত বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃতি। এ যেন মাতৃক্রোড়ে বসে মাকেই অস্বীকার! তাই তো বোশেখি বাঙালি ধরাচুড়ো ছেড়ে শুধুই তাপ্পিমারা পোশাকি বাঙালি।
আমার থেকে পৌনে তিন বছরের বড় দাদা প্রণাম আদায়ে বিশেষ উৎসাহী ছিল। আর পয়লা বৈশাখ পার হওয়ার আগেই নব্বই কিলোমিটার দূরের গ্রাম থেকে মামাতো দিদির আশীর্বাদ-চিঠি চলে আসত। আমাকে কেউ কখনও প্রণাম করত না। আমার সাড়ে পাঁচ বছরের কনিষ্ঠা ভগ্নির উপরে একবার দাদাগিরি ফলাতে গিয়েছিলাম। প্রণাম তো করলই না, উল্টে প্রচণ্ড খিমচে দিল। সে-দাগ এখনও আছে।
নববর্ষের ক্ষেত্রে দেবদ্বিজে ভক্তিটা অত প্রকট না। সেক্যুলার বাঙালির মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় ভাল। দেবতাদের যা শুনি, আহারের চেয়ে বিহারেই উৎসাহ বেশি। নববর্ষে আবার গুরুজনদের পেন্নাম আর চিঠি লেখা ছাড়া সমশ্রেণির আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোলাকুলির ব্যাপারটাও ছিল। তবে সময়বিশেষে সংস্কৃতিটা নিত্যবস্তু, অর্থাৎ, তার যাবতীয় আনুষঙ্গিক নিয়ে সব সময়েই উপস্থিত।
গর্ব জিনিসটা নিচুস্তরের অনুভূতি। ওটা না থাকলেই ভাল। যদি বঙ্কিম-নজরুল-রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভুলে গিয়ে ‘আরে ইয়ার’ জাতীয় হিংরিজিকে মাতৃভাষা বলে আমরা বরণ করি, তা হলে আমাদের সাংস্কৃতিক গতিটা সভ্যতা থেকে অর্ধসভ্যতার দিকে চলমান ধরে নিতে হয়। শুভ দিনে বাংলায় গুরুজন, প্রিয়জনকে চিঠি লেখা, গুরুজনদের প্রণাম, প্রিয়জনদের আলিঙ্গন, নিজেদের ভাষায় বাক্যালাপ- এই সব প্রথা জীবনকে সানন্দ করে।
ধরা যাক, সুদূর ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে অ্যাং এসেছে বঙ্কুবাবুকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে। এখন যদিও আর আগের মতো নববর্ষের প্রণাম, মিষ্টির আদানপ্রদান, কোলাকুলি অতটা নেই, তবে অত্যধিক ‘বং’ হতে গিয়ে ‘শুভ নববর্ষ’ যেন ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ না হয়ে যায়! বাঙালির একান্ত ঘরের এই উদযাপনের সেই মাটির গন্ধ যেন বজায় থাকে চিরকাল…