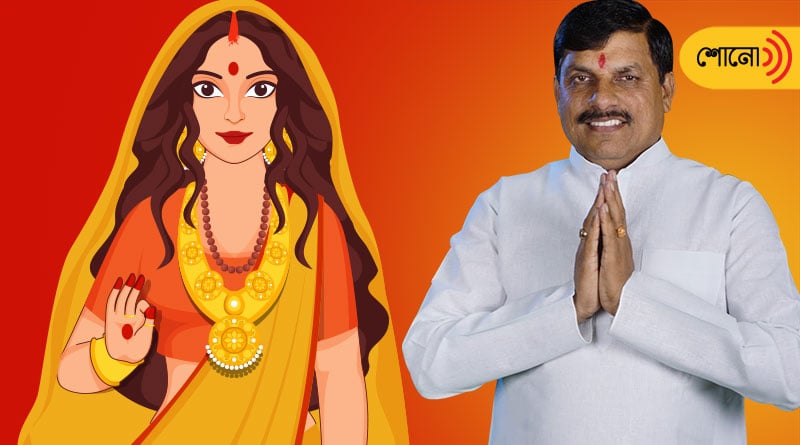কবিতা মাথায় এলে আভেন নিভিয়ে লিখে নেব, বলেছিলেন দেবারতি
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: January 11, 2024 8:03 pm
- Updated: January 11, 2024 9:05 pm


‘কী বলব আমি? আমি কি পারব? তোমরা সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করবে, সে জিনিস আমি জানি না।’ – বলেছিলেন দেবারতি মিত্র। কবিতা স্পর্শ করে কাটিয়ে দেওয়া এক আটপৌরে জীবন। কবিতাকে সঙ্গী করেই যৌথ ‘যোগিয়া’-যাপন। যে জীবন কোনও আন্দোলনমথিত নয়, এককের। সাক্ষাতের সেই মুহূর্তে পাড়ি দিলেন সম্বিত বসু।
বছরখানেক আগের এক দুপুরবিকেল। উপস্থিত হয়েছি যোগিয়াবাড়িতে। মণীন্দ্র গুপ্ত এবং দেবারতি মিত্রর বাড়ি। সঙ্গে সত্তরের কবি, অরণি বসু। মণীন্দ্রবাবু শুয়ে আছেন বিছানায়। ক’দিন আগেই নাকি বিছানা থেকে উঠে অনেক বইপত্র ঝেড়ে-টেড়ে পরিষ্কার করে রেখেছেন। তারপর আবার বিছানায়। তখন ‘শিলাদিত্য’ পত্রিকার এক শারদ সংখ্যায় ‘নুড়ি বাঁদর’ উপন্যাস পড়ে এক রাতে আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা! কথা মণীন্দ্রবাবু প্রায় বলছেনই না, দেবারতিদিই টুকটাক। সবই সাংসারিক, গৃহসম্বন্ধীয় কথা। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলে যেমনটা হয়। এর-ওর কথা জিজ্ঞেস করে, ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করে, চা করতে উতলা হয়ে পড়ে। দেবারতিদিও সেদিন ছিলেন সেইরকম। সেই প্রথম দেখা, অবয়বে আটপৌরে ছাপ। আলগা যত্নে ভেতরে ঢেউ উঠছে। এই সেই কবিদম্পতি। এই সেই ‘অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজে’র লেখক। এই যিনি শুয়ে আছেন, নিরুপদ্রব, তিনি বাংলা ভাষায় ওইরকম একটা ভয়াবহ উপদ্রবের উপন্যাস লিখেছেন!

লেখা প্রসঙ্গে কথা তুলেছিলাম আমিই। মণীন্দ্রবাবুকে বলেছিলাম ওই উপন্যাস ভালো লাগার কথা। শুয়ে শুয়ে মণীন্দ্রবাবু বললেন, ‘ভালো লেগেছে? আসলে এখন কোথাও তো বেরতে পারি না, মনে হয় এটা হলে কী হত, ওটা হলে কী হত…’। দেবারতিদি, আমি, অরণিদা সেই মৃদুস্বরের কথা বলার সামনে স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। আর বিকেল গড়াতে গড়াতে সন্ধে নেমে আসছিল এই যোগিয়াবাড়িতে। যে কথা বলে বলুক, আমি ঠায় বসে, মেপে নিচ্ছি সেই দম্পতির ঘরের আভা। ওষুধের গন্ধ। তাকে কী কী বইয়ের মলাট সোজা করে রাখা। কোন কোন বই স্পাইনের দিক করে। না, দেবারতিদি কিংবা মণীন্দ্র গুপ্তর কোনও বই-ই সেই তাকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখতে পাইনি। দেখছি, লাগোয়া বারান্দায় দু’জনের জামাকাপড় শুকিয়ে গিয়েছে হঠাৎ হাওয়ায় উড়ছে। ভাড়া করা কোনও লোকদেখানো নির্জনতা ছিল না মণীন্দ্রবাবু কিংবা দেবারতি মিত্রর জীবনে। তাঁদের নির্জনতার মালিক ছিলেন তাঁরাই। এমনকী, সেই ঐকান্তিক ঘরেও।
এর মাঝে দুম করেই মণীন্দ্রবাবু তাঁর বিছানা চিরকালের জন্য ফাঁকা করে দিলেন। এমনই এক ব্যর্থ জানুয়ারি মাসে, ৩১ তারিখ, ২০১৮ সালে। ছোট ঘরে দেবারতি মিত্র একা। ফোনে যে কথা হয় তা নয়, কিন্তু ওই অরণিদা মারফত। তিনিও খবর নিচ্ছেন, আমিও নিচ্ছি। একদিন ঠিক করা হল, সংবাদ প্রতিদিন-এর ‘ছুটি’র জন্য একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। করলাম ফোন। দেবারতিদি চমৎকার আপত্তি করতে পারতেন। বারেবারেই বলতে লাগলেন, ‘আমি কি অত জানি?’ বললাম, ‘আড্ডা মারব, একটা-দুটো কথা বলব।’ অবশেষে কোনও দৈব প্ররোচনায় দেবারতিদি রাজি! হয়তো খানিক গল্প হবে, দেখা হবে– এই বোধও কাজ করছিল ওঁর।
বেলা করে গিয়েছি। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর। দেবারতিদিকেও সেইমতো বলা। ঘরে বসতে না বসতেই দেবারতিদি আবারও শুরু করলেন, ‘কী বলব আমি? আমি কি পারব? তোমরা সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করবে, সে জিনিস আমি জানি না। আর আমি যা বলব, তা কি লোকে পড়বে? কী হবে সেসব ছেপে?’ ছবি তোলার সময়ও একইরকম ছটফটানি। ‘আমার ছবি! সে কী!’

তারপর যখন কথা শুরু হল, নেহাত আড্ডাছলেই উঠে এল তাঁর কথা, কবিতার কথা, মণীন্দ্রবাবুর কথা। না, মহাজীবনটিবন নয়। একেবারেই আটপৌরে এক বাঙালির কথা। যাঁকে কবিতা এসে স্পর্শ করে গিয়েছিল, তারপর স্পর্শবিমুখ হওয়ার আর কোনও ক্ষমতাই ছিল না। যে জীবন কোনও আন্দোলনমথিত নয়, এককের। বিশ্বাস করতেন ‘সবমেত ধ্যান’ বা ‘সমবেত কবিতাচর্চা’ বলে কিছু হয় না। যে জীবন লেখালিখির জন্য পুরস্কৃত হতে ভয় পায়। শুধু মনে রেখেছিলেন, মণীন্দ্র গুপ্তর বলা কথা, যিনি দেবারতিদিকে ক্রমাগত বলে চলেছিলেন, ‘লেখো লেখো। লেখাটাই তোমার আইডেনন্টিটি।’ অথচ লেখা ক্রমে কমিয়ে দিয়েছিলেন দেবারতি মিত্র। বলছিলেন, বেরচ্ছেন না, তাই লেখা হচ্ছে না। কোনও একটা দৃশ্য দেখে স্ফুরণ হলে তবে তো লিখবেন! কিন্তু সেরকম কিছুই আর ছুঁয়ে দিচ্ছে না তাঁকে। তাই বলে পড়া, কবিতা পড়া, বন্ধ করে দেননি। রোগা, হঠাৎ বদলে যাওয়া সেই মুখ, আত্মপ্রত্যয়ে বলে উঠেছিল, ‘বোধহয় অনেক কমবয়সিরাও এত কবিতা পড়ে না।’ অবশ্য এ-ও বলেছিলেন, একইরকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, যে, রান্না করতে করতে কবিতার পঙ্ক্তি মাথায় এলে আভেন নিভিয়ে লিখে নেবেন।
দেবারতিদি চলে গেলেন। ব্যর্থ জানুয়ারি মাস হয়তো এবার সফল হল। মিলিয়ে দিল মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে। শ্মশানে দেহ পোড়ে, জীবনপ্রণালী পোড়ে না। অন্ধ স্কুলে যে ঘণ্টা বাজছে, তার শব্দ বাংলা কবিতায় ছড়িয়ে পড়েছে অনেক আগেই, তাকে আর থামানো যাবে না।