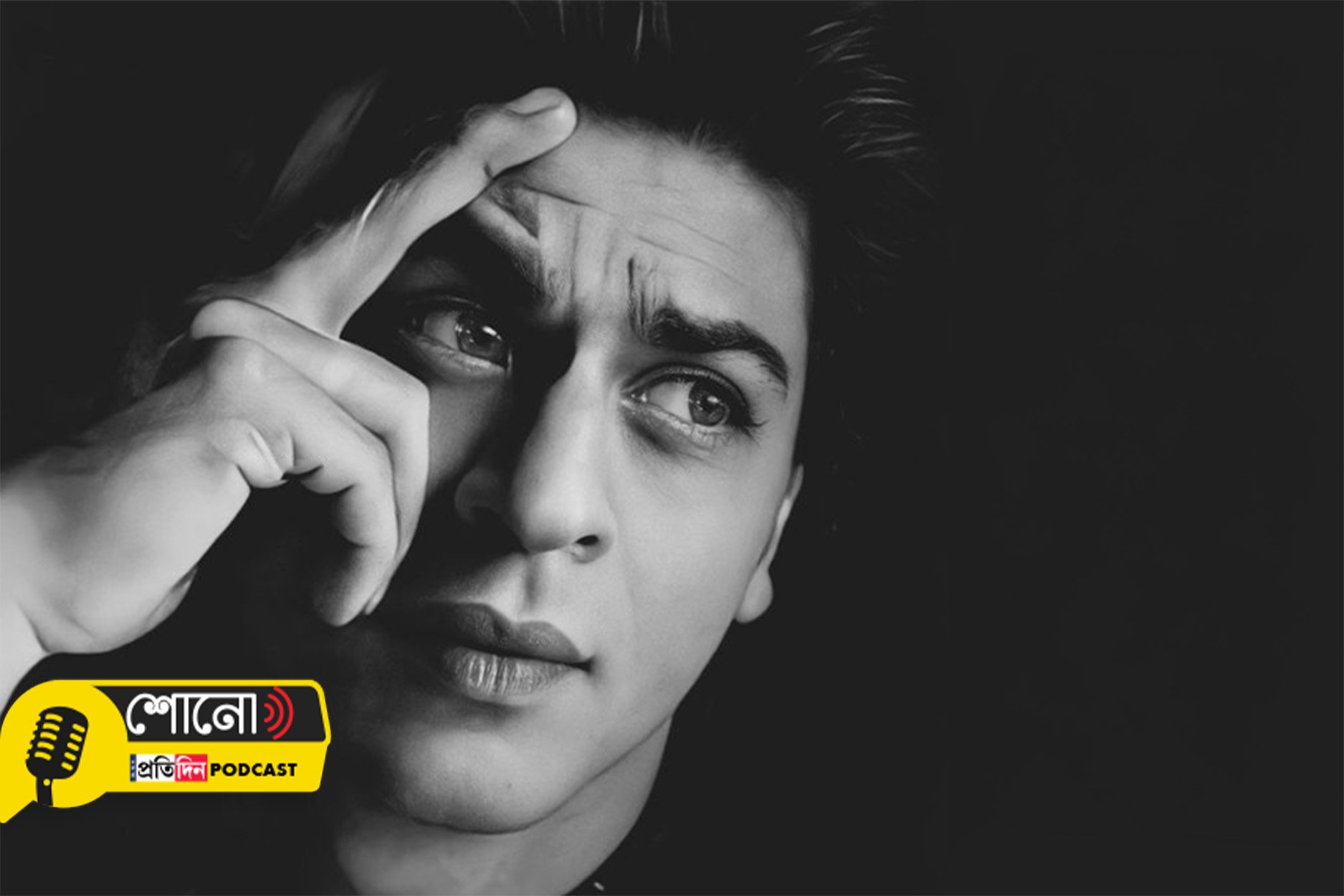মূর্তি নেই, আছে কল্পনা… অরূপের মাঝে রূপের সাধনার হদিশ শিবলিঙ্গ অর্চনায়
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: February 26, 2025 8:29 pm
- Updated: February 26, 2025 9:40 pm


যিনি বিমূর্ত, তাঁকেই আমরা কল্পনা করে নিই মূর্তির মধ্যে। আবার সর্বদা যে সেই মূর্তির সামনেই সমর্পণ, তা কিন্তু নয়। যেখানে মূর্তি নেই, সেই নিরাবয়বের মধ্যেও অবয়ব কল্পনা করে নেয় আমাদের মন। এই যে শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের পুজোর চল চলে আসছে আদি-অনন্তকাল ধরে, তা নিয়ে তো কখনও ভুরু কোঁচকায়নি কেউ। লিখছেন, সুলয়া সিংহ।
রূপের মাঝে অরূপের সাধনা। আবার উলটোটাও। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় কল্পনা আর বিশ্বাস যেন এভাবেই হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে। যিনি বিমূর্ত, তাঁকেই আমরা কল্পনা করে নিই মূর্তির মধ্যে। আবার সর্বদা যে সেই মূর্তির সামনেই সমর্পণ, তা কিন্তু নয়। যেখানে মূর্তি নেই, সেই নিরাবয়বের মধ্যেও অবয়ব কল্পনা করে নেয় আমাদের মন। এর বীজ আমাদের ভাবনার গহনে। তার সবথেকে গ্রাহ্য উপমা বোধহয় শিবলিঙ্গ অর্চনার রীতি।
মন্দির যেমন ভক্তির, তেমন শিল্পরূপেরও পাঠশালা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মন্দির রূপের ধারণা দেয়। সে রূপ কার? না, যিনি নিরাকার। যাঁকে আকার বা অবয়বে ধরা যায় না। তবে, মানুষের কল্পনার প্রসার এতখানি যে, তা নিরাকারকে একটি অবয়বে, একটি পরিধিতে, এবং বিশিষ্ট রূপে কল্পনা করতে পারে। দুর্গা, মহাদেব, কালী, লক্ষ্মী-নারায়ণের যে রূপ আমাদের কল্পনায় ভাসে, তার বীজ রয়ে আছে এখানেই। সেই রূপেই আসে ভক্তি। এ আসলে আমাদের মননের এক সম্মিলিত ভুবন। যেখানে দেবতাদের রূপ-কল্পনা একটি প্রকল্প হয়ে আছে।
তবে, বলার কথা এই যে, সেই প্রকল্প একমাত্রিক নয়। তার এক অন্য চলনও আছে। তাও আছে আমাদের চোখের সামনে, বলা যায় এই প্রকৃতির পাঠশালাতেই। যে ভক্তির প্রসঙ্গ এল, সেই সূত্রেই বলা যায়, ভক্তি তো রূপ থেকে আমাদের অরূপেই পৌঁছে দেয়। মূর্তির মাধ্যম থেকে আমাদের গন্তব্য হয়ে ওঠে বিমূর্তের উদ্দেশে। অতএব এ-প্রশ্ন বোধহয় অসঙ্গত নয় যে,
ভক্তি কি সত্যিই রূপ খোঁজে? এই বিপ্রতীপ চলনের উদাহরণ কিন্তু অপ্রতুল নয়। বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে রাখা তিনটি প্রস্তরকে দেবকল্পনা করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেও কুণ্ঠা বোধ হয় না। কালীঘাটের যে বিরাট পাথর, তাই-ই আমাদের কাছে দেবীরূপ। পাড়ার মোড়ের গাছের নিচে বেদি বানিয়ে পাথরই পূজিত হয় বজরংবলি রূপে। নারায়ণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় শালগ্রাম শিলায়। এখানে রূপের প্রকাশ নেই। তা বলে রূপ কি নেই? আছে আমাদের কল্পনায়। এখানে আমাদের সাধনা যেন অরূপের মধ্যে রূপের সন্ধান। মানুষের কল্পনার জোর ঠিক এতখানিই। যেখানে মূর্তি নেই, সেখানেও মূর্তির কল্পনা অসম্ভব নয়। শিবলিঙ্গ অর্চনা বোধহয় এর সবথেকে বড় উদাহরণ। শিবের নানারকম মূর্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত। রূপের সেই বহুধা বিস্তার সঞ্চিত আছে আমাদের কল্পনায়। অথচ সামনে থাকে শিবলিঙ্গ-রূপ শিলাখণ্ডটি। তাতেই রূপের কল্পনা যেন আমাদের আধ্যাত্মিকতারই এক জোরালো কাঠামো।
আরও শুনুন: সভ্যতাকে জল দেন, সভ্যতার বিষও পান করেন যিনি তিনিই শিব
কলকাতার দুর্গাপুজোর থিমের ভিড়ে অনেক সময়ই দেবী দুর্গার রূপের বদল ঘটলে রে রে করে ওঠেন অনেকে। ভক্তিতে নাকি বাধা হয়ে দাঁড়ায় দেবীর পালটে যাওয়া বা বলা ভালো খানিক অচেনা রূপ। কিন্তু এই যে শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের পুজোর চল চলে আসছে আদি-অনন্তকাল ধরে, তা নিয়ে তো কখনও ভুরু কোঁচকায়নি কেউ! শিবলিঙ্গ ও যোনির সেই অবয়বের মধ্যেই ভক্তরা শিব-পাবর্তীর রূপের সন্ধান পান। পুজোশিল্পী সুশান্ত পালকেও নিজের বিমূর্ত দুর্গা ভাবনার জন্য নানা বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রতিমা নিয়ে তথাকথিত পরীক্ষানিরীক্ষা করা নিয়ে উঠেছে আপত্তিও। কিন্তু শিল্পী দেবীকে খুঁজে পান নিজের মনের মধ্যে। বিশ্বাস করেন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। একজন নারী, এমনকী একজন পুরুষের মধ্যেও দুর্গার বাস। তাই তিনি ঈশ্বরের রূপকে চেনা ছকের বাইরে ভাবতে ভালোবাসেন। তাঁর দুর্গাযাপনে ঐশ্বরিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্যভাবে। তাই তো নিজের নামের সঙ্গেও জুড়ে ফেলেছেন দুর্গাকে। সুশান্ত শিবাণী পাল হিসেবেই পরিচিত হতে চান তিনি। শিল্পীর কথায়, আমরা যে সবসময় কোনও মূর্তির সামনেই দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করি, এমনটা তো নয়। একটা পাথরের মধ্যে মূর্তিকে কল্পনা করার অভ্যেস আমাদের চিরকালীন। তাতে ভক্তিতে ভাটা পড়ে না।
তাছাড়া দুর্গার মন্ত্রেই তো রয়েছে সেই ব্যাখ্যা- ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা স্ত্রীয় পশুশ্চ নরশ্চ দুর্গা। যদ্ যদ্ধি দৃশ্যং খলু তদ্ধি দুর্গা দুর্গা স্বরূপাৎ নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ। অর্থাৎ পঞ্চভূতাদি দুর্গা, চতুর্দশ ভুবনসমূহ দুর্গাময়, স্ত্রী পশু নর সকলেই দুর্গা, জগতে যা কিছু আছে সবই দুর্গা, দুর্গা হতে ভিন্ন জগতে আর কোন তত্ত্ব নেই। তাই তো বিপদে-আপদে কিংবা কৃতজ্ঞতায় চোখ বন্ধ করে নিজের আরাধ্য দেবতার চেহারা ভেবে নিয়েই প্রার্থনা করতে অভ্যস্ত আমরা। তখন সম্মুখে মূর্তির খোঁজ করে না কেউ। নিরাবয়বে অবয়ব কল্পনায় কোনও অসুবিধা হয় না।
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার এক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছিলেন কীভাবে তিনি পাথরের মূর্তির মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন পান। বলেছিলেন, কলসে জল রাখা হয়। সেই কলস থেকেই আমরা জল খাই। কলস তো খাই না। তেমনই মূর্তির মধ্যে পাথর আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা পুজো করি তার মধ্যে যে চেতনা বা ঈশ্বর আছেন, তাঁকেই।
কেউ পাথরে ভগবানকে খুঁজে পায়, আবার কেউ ভগবানের মধ্যেও পাথরই দেখতে পায়। এ তর্ক আজীবন চলবে। তবে বিশ্বাস ও অনুভূতিই প্রকৃত ঈশ্বর। মাধ্যম যেমনই হোক না কেন, আমরা উপাসনা করি সেই সত্য-সুন্দর ও শিবকেই।