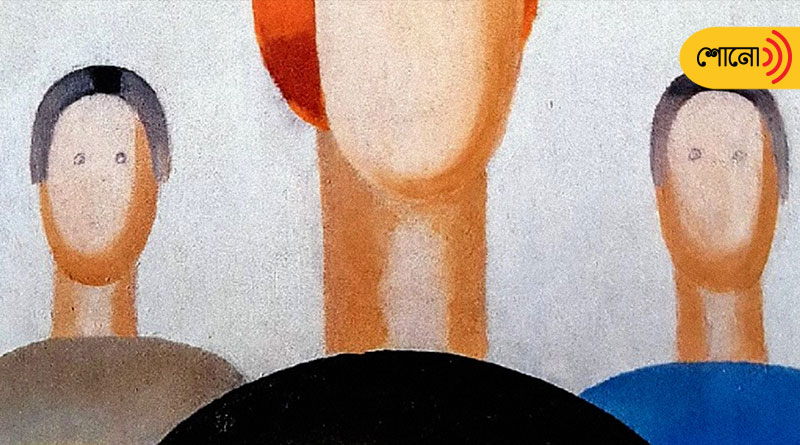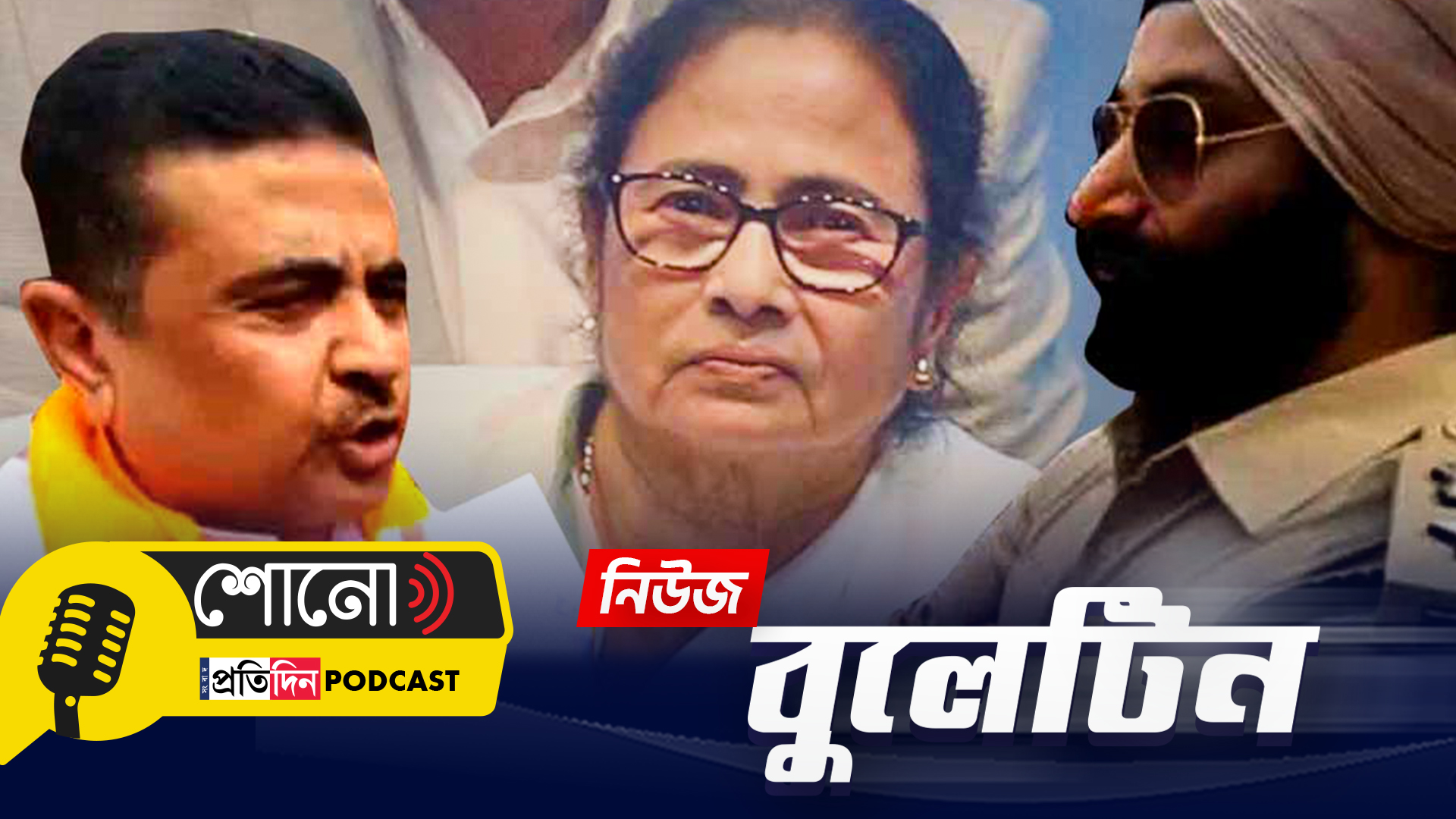খ্যাপামি থেকে সাম্প্রদায়িক অশান্তি, উগ্র ভারতের ছক বুঝতে বারবার ভুল উদার দেশের?
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: March 19, 2025 3:43 pm
- Updated: March 19, 2025 8:14 pm


‘মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা উদ্ভট ধারণা আছে যে, শিল্প মূল্যায়নের এই ধরো-মারো-পোড়াও পদ্ধতিটা সংঘ পরিবারের কিছু খ্যাপাটে লোকের কুঅভ্যাস মাত্র। তাঁরা বোঝাতে চান এগুলো নিছকই কিছু তুচ্ছ ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিছু লুম্পেন পাগলাটে লোক এসব করে বেড়ায়, সংঘ পরিবারের বিবেকবান ও পরিশীলিত সদস্যদের সঙ্গে এদের এক করে দেখা উচিত নয়। এদের কাছে একটা খবর বোধহয় পৌঁছে দেওয়া দরকার– এই পাগলরাই গোটা ময়দান দখল করে নিয়েছে।’ – সদানন্দ মেননের এই কথা আজ দেশে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।
ইতিহাস জানে না! নাকি, উন্মাদ? ‘শিক্ষিত’ ভারতবাসী যতক্ষণে বিস্ময় প্রকাশ করে ‘যাও পড়তে বসো’ নিদান দেয় সোশ্যাল মিডিয়ায়, ততক্ষণে দেশের ইতিহাসকে নিজের মতো করে ভেঙেচুরে গড়ে নেয় একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী। সাম্প্রতিক এই ইতিহাসের বারবার পুনরাবৃত্তি, একই রকম উন্মাদনার অতিমারী! তবু ভ্যাকসিন মেলে না।
‘ছাবা’ থেকে নাগপুর দাঙ্গার এই পর্বটি কি নতুন ভারতের কাছে অচেনা! তা বলা যায় না। বিশেষ করে, যে দেশের ইতিহাসে বাবরি-ধ্বংসের লজ্জা আছে, তার তো এই পথ চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। সিনেমা মুক্তির সময় থেকেই বলা শুরু যে, এই হল ‘আসল’ ইতিহাস। অর্থাৎ যে-ইতিহাস চাপা দেওয়া হয়েছে। সেই গৌরবময় অতীত পুনরুদ্ধার। ঔপনিবেশিক পর্বের ভারতে তার গুরুত্ব ছিল অন্যরকম। স্বাধীন ভারতে তা হয়ে দাঁড়াল আর এক জিনিস! তবে কোনওটিই কার্যকারণ বিচ্ছিন্ন তো ছিল না। আনন্দমঠের আশায় যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তা যে বিষবৃক্ষ হয়ে উঠতে পারে, এমন সম্ভাবনা দেখেও দেখা হয়নি। বুঝে-শুনেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বরং। একা রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা মস্ত অংশ জুড়ে সেই বিপদের কথা মনে করিয়ে করিয়ে দিতে দিতে অবশেষে যেন নির্বাসনই নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের শালবনে। ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে ‘গুরুদেব’ বানিয়েছে; ‘মহাত্মা’ ভাবেনি, সেদিনও নয়, এখনও নয়। ফলত যে-চাকা গড়ানোর ছিল, তা গড়িয়েছে।
:আরও শুনুন:
অলকা ইয়াগনিকের ‘ফ্যান’ ছিলেন লাদেন! কুখ্যাত জঙ্গি সম্পর্কে কী ভাবতেন গায়িকা?
পুরনো কাসুন্দি বিস্তারিত না ঘাঁটলেও ভারতবাসী আজ জানে, কী হইতে কী হতে পারে। ইতিহাস নির্মাণের গোড়াতেই তাই থাকে কোনও এক গৌরবের ইতিহাসকে খুঁড়ে তুলে আনার গপ্পো। জাতীয়তাবাদী হেমলক চারিয়ে দেওয়ার এই প্রাথমিক ধাপ। ঘটনা হল, এই একই কায়দা এতবার অনুসৃত হয়েছে যে, আগাম সতর্ক হওয়াই উচিত ছিল। সিঁদুরে মেঘ আর ঘরপোড়া গরুর প্রবাদ তবু বর্তমান ভারতে যেন কিছুতেই খাটে না। অতএব সিনেমা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কিছু অদ্ভুত দৃশ্যের জন্ম। দেখা গেল, এক ব্যক্তি একেবারে সাম্ভাজি মহারাজ সেজে নাগপুরের সিনেমাহলে হাজির হয়েছেন। একজন ক্লাইম্যাক্স সহ্য করতে না পেরে হলের ভিতর দারুণ ভাঙচুর করেছেন। কখনও গ্রামে গিয়ে গুপ্তধন সন্ধান করা হয়েছে। এমন নয় যে, এসব খবর চাপা ছিল। যখন তা সামনে এসেছে, বড় অংশের মানুষের কাছে তা ‘পাগলামি’ হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে। আরও একটু পরে যখন সরাসরি রাজনীতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল, তখন বোঝা গেল, ওই ভেবে নেওয়া ‘পাগলামি’ আসলে এক রাজনৈতিক কৌশলের নান্দীমুখ। আগ্রা দুর্গে শিবাজির জন্মদিন পালনে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পাশে ডেকে নিলেন ভিকি কৌশল-কে। ধরে নেওয়া যায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ততার কারণে খুব কম সিনেমাই দেখার সময় পান। তা তিনি এ সিনেমা দেখলেন, এবং অভিনয় ইত্যাদির প্রশংসাও করলেন। মার্চের গোড়াতে যখন পুরোদস্তুর রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠল এই প্রসঙ্গ, এবং ঔরঙ্গজেবের সমাধি উড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব হাওয়ায় ভাসতে শুরু করল, তখন যেন নাগরিক সমাজ আর একবার বিস্মিত হল। গোড়ার সেই ‘পাগলামি’ প্রতিরোধে এতক্ষণে ইতিহাসের টীকা তুলে ধরার চেষ্টা হল। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ফিরে এসেছে আগুনের চাকা। ফলশ্রুতি, নাগপুরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি।
:আরও শুনুন:
ফেরা আর নিজেকে ফিরে পাওয়ার গল্পেই একটুকু শান্তি খোঁজে জীবন
দেখা যাচ্ছে, এই গতিবিধি জেনেও বারবার দেরি হয়ে যাচ্ছে উদার ভারতের। যে-ভারত ধর্মীয় উন্মাদনা চায় না, মুসলিমকেই একমাত্র শত্রু হিসাবে দেখতে চায় না, সেই ভারতও যেন বুঝতে পারছে না যে, ওই তথাকথিত ‘পাগলামি’ আসলে আগুন লাগানোর গোড়ার কথা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভিজাত উন্নাসিকতা যেন এই বোঝার পথে অন্তরায়। সদানন্দ মেনন বলেছিলেন, ‘মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা উদ্ভট ধারণা আছে যে, শিল্প মূল্যায়নের এই ধরো-মারো-পোড়াও পদ্ধতিটা সংঘ পরিবারের কিছু খ্যাপাটে লোকের কুঅভ্যাস মাত্র। তাঁরা বোঝাতে চান এগুলো নিছকই কিছু তুচ্ছ ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিছু লুম্পেন পাগলাটে লোক এসব করে বেড়ায়, সংঘ পরিবারের বিবেকবান ও পরিশীলিত সদস্যদের সঙ্গে এদের এক করে দেখা উচিত নয়। এদের কাছে একটা খবর বোধহয় পৌঁছে দেওয়া দরকার– এই পাগলরাই গোটা ময়দান দখল করে নিয়েছে।’ স্বভাবতই সেই ময়দানের বাইরে দাঁড়িয়ে অনন্ত পাগলামি তথা নাগপুর-পরিণতি দেখে যাওয়া ছাড়া এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তথা উদারতাবাদী ভারতের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি যে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভারতকে সুবিধা করে দিচ্ছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ইতিহাসবিদ, সমালোচক, প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার যাবতীয় আয়োজন সারা। যে কোনও মূল্যে যুক্তি-তর্ককে ধূলিসাৎ করে দেওয়াও এখন স্বাভাবিক। এই প্রায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত সময়ে একমাত্র গোড়ায় সতর্ক হয়ে আগুনে জল ঢালাই উপায় হতে পারে। অথচ আগুন জ্বালানো আর আগুন নেভানোর কাজের মধ্যে বিস্তর পথে এল দেরি! যদি রাজনৈতিক দলের উপর ভরসা না-ও থাকে, মানুষ কি প্রতিরোধে নিজের উপরও নিজে ভরসা করতে পারছে! এ-প্রশ্নই বোধহয় আজ সবথেকে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।
:আরও শুনুন:
কোভিড গিয়েছে, আতঙ্ক গিয়েছে, দুর্বলতা এসেছে
অথচ ইতিহাস হাতে ছিল। যদি ঔরঙ্গজেবের সমাধি ধ্বংস করে দেওয়াই কাজের কাজ হত, তাহলে শিবাজির বংশধররাই তা করতে পারতেন। করেননি। বরং শিবাজির পৌত্র, সাম্ভাজির পুত্র শাহু(১) যিনি মুঘলদের হাতেই বন্দি ছিলেন, নিজে গিয়ে ঔরঙ্গজেবের কবরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছিলেন। মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত ‘মারাঠা কালখণ্ড’ (ভি.জি খোবরেকর) বইতেই এর উল্লেখ আছে। রিচার্ড এটনের ‘আ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ ডিকান’ বইটিও একই ঘটনার সাক্ষী দিচ্ছে। আজকের হিন্দুত্বে শিবাজির প্রপৌত্র সম্ভবত পাশ করতেন না। তাঁর মারাঠা পরিচয়পত্র হয়তো কেড়ে নিত এই পরিকল্পিত ‘পাগলামি’। যে তথাকথিত ‘পাগলামি’ কেড়ে নিচ্ছে ভারতকেও। আর চেনা জিনিস নতুন করে চিনতে ভুল হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।
‘ছাবা’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। ভালোবাসার দিন এই ভারতে একটি দাঙ্গার সূচনাদিন হিসাবেও চিহ্নিত হয়ে থাকল। আক্ষেপ আছে, তবু পদক্ষেপ নেই।