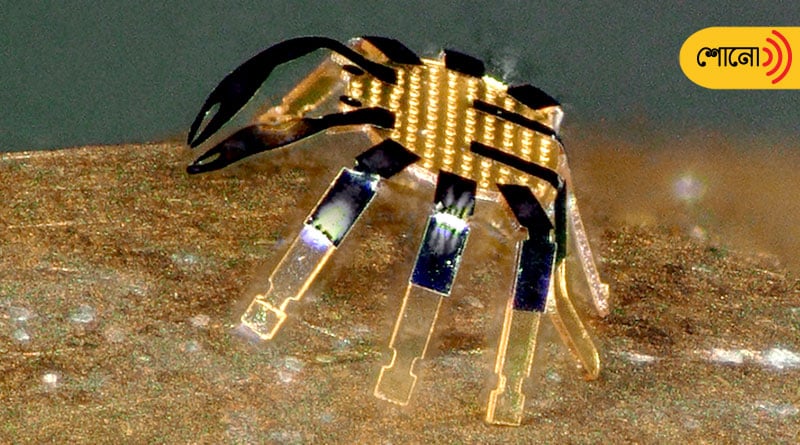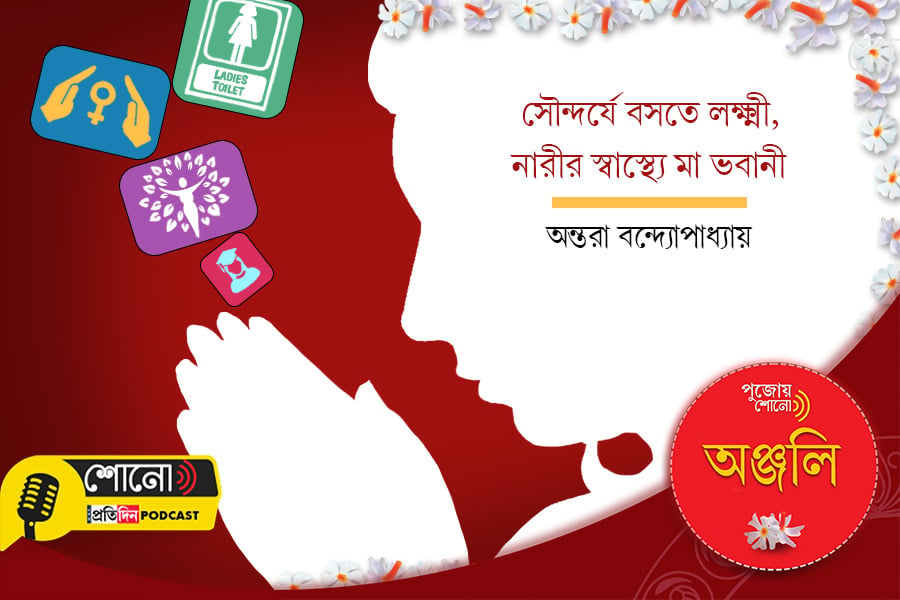দুই আত্মহত্যা, দুই বাস্তবতা, তবুও জীবন সিসিফাস
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: March 20, 2025 7:29 pm
- Updated: March 20, 2025 7:29 pm


জীবন আর জীবনের মর্ম মুখোমুখি বসে সেদিন পাশা খেলে। আর কার দানে কখন যে কে হেরে যায়, এই পৃথিবী কোনোদিন তার হদিশ পায় না। ফলত জীবনের এই দারুণ পানশালা ছেড়ে কেউ কেউ পাড়ি দেন। পড়ে থাকে এই অস্তিত্বের পৃথিবী। হননের এই কীট কাউকে কাউকে কুরে কুরে খায়। নিজেকে হত্যার শিল্প জেগে ওঠে নিজেরই হৃদয়ে। আত্মহত্যা এককের, তবু আত্মহত্যা ব্যাপক অর্থে একাকীর নয় কখনওই। ছবি- দীপঙ্কর ভৌমিক।
নিজেকে হননের খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছেন যাঁরা, জানেন, হয়তো, ফড়িঙের ডানাতেও এ-জীবন দেয় ডাক। সে-ডাক কি বেজে ওঠে না সকলের প্রাণে! বোধহয় আরও কোনও অনতিক্রম্য হাতছানি উপেক্ষা করতে না-পেরেই মানুষ ফুরিয়ে ফেলেন নিজেকে। একদিন, অকস্মাৎ। অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতা পেরিয়ে কোনও এক পঞ্চমীর রাতে মরিবার হয় তার সাধ। সকলে নয়, কেউ কেউ, এগিয়ে যান সেই পথে। বেঁচে থাকা পৃথিবী তখন দুঃখিত, বিস্মিত, বিমর্ষও। মৃত্যুর আশ্চর্য গন্ধমাখা এ-জীবনকে নিয়ে নতুন করে তাই ভাবতে বসা। তবু যে মৃত্যু, যে অমোঘ হননেচ্ছা একজন সহ-নাগরিককে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তার কূলকিনারা মেলে না। বিস্ময়ের এই যে, এই অফুরন্ত জীবনের উৎসবের ভিতর সে-ইচ্ছা থেকেই যায়। ভারি সঙ্গোপনে। জীবন-মৃত্যুর এই রহস্য বোধহয় মীমাংসাহীন।
অথচ অর্থহীনতায় আক্রান্ত এই ‘অ্যাবসার্ড’ জীবন জানে ‘there is but one truly serious philosohical problem, and that is suicide.’ মোকাম ছেড়ে বয়ে যাওয়া মানুষ দিনে দিনে হয়ে ওঠে আদতে অ্যাবসার্ড। তার স্মৃতির পিনকোড যায় হারিয়ে। ভবিষ্যতের লাইটহাউস চোখে পড়ে না। তার সত্তা আর তার উৎপাদনের ভিতর কোনও যোগসূত্র থাকে না। তবু, প্রতিদিন একই বেঁচে থাকার রুটিন। বিচ্ছিন্নতা-জাত এই অ্যাবসার্ডিটি জীবনেরই দান। সে-পাথর ঠেলতে ঠেলতেই অগণন মানুষ বাঁচে। তবু, ‘what is called a reason for living is also an excellent reason for dying’- এরকমটাও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, অন্তত কারও কারও কাছে। একদিন তাই সেই অ্যাবসার্ড মানুষ যেন বুঝে যায় ‘জাগিবার গাঢ় বেদনার/ অবিরাম- অবিরাম ভার / সহিবেনা আর-‘। জীবন আর জীবনের মর্ম মুখোমুখি বসে সেদিন পাশা খেলে। আর কার দানে কখন যে কে হেরে যায়, এই পৃথিবী কোনোদিন তার হদিশ পায় না। ফলত জীবনের এই দারুণ পানশালা ছেড়ে কেউ কেউ পাড়ি দেন। পড়ে থাকে এই অস্তিত্বের পৃথিবী। হননের এই কীট কাউকে কাউকে কুরে কুরে খায়। নিজেকে হত্যার শিল্প জেগে ওঠে নিজেরই হৃদয়ে। আত্মহত্যা এককের, তবু আত্মহত্যা ব্যাপক অর্থে একাকীর নয় কখনওই। অস্তিত্বের যে ভার অসহ হয়ে ওঠে, যে আত্মবিচ্ছিন্নতা মানুষকে ঠেলে দেয় অমোঘ সিদ্ধান্তে, তার জন্ম এই মানুষেরই সমাজে। আত্মহত্যা তাই বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সর্বতোভাবেই সামাজিক ঘটনা।
সাম্প্রতিক দুটি আত্মহত্যার ঘটনা যেন তাই ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে বাস্তবতার সেই নিষ্ঠুরতাতে। খবরে প্রকাশ, কলকাতায় একজন আইটি কর্মী তাঁর নিজের অফিসের ছাদ থেকেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে যে, মানসিক অবসাদ কারণ হতে পারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। বুধবার সন্ধের এই ঘটনার পর থেকেই, নানা মহলের আলোচনায়, ঝাঁ-চকচকে জীবনের ভ্রম উঠেছে কাঠগড়ায়। বিশ্বায়ন যে বিচ্ছিন্নতা ডেকে এনে উপহার দিয়েছে এক ‘অলৌকিক’ জীবনের খোঁজ, সেই মরীচিকায় নেই জলের সন্ধান। অর্থের হাতছানি যে চাপের ভিতর মানুষকে নিয়ে গিয়ে ফেলছে, তা ক্রমশ মানুষকেই যেন খাটো সংকুচিত করে অবমানবে পরিণত করেছে। আইটি কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত। প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে আসে বটে। তবে শারীরিক স্বাস্থ্যের মতো, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ যতটা গুরুত্ব পাওয়ার কথা, এখনও তা পায় না। ফলত একদিকে বহমান জীবন। জীবনের তথাকথিত জৌলুস। অন্যদিকে নিজেকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলা এই জনতাজঙ্গলের বিষাদময়তায়। এই বাস্তবতার ভিতর ঠিক কোথায় যে কার ট্রিগার-বিন্দু রয়ে আছে, তা কে জানে! আইটি-কর্মীর আত্মহত্যা মনে করিয়ে দিচ্ছে, মানবসম্পদ নেহাত একটি শব্দ মাত্র নয়। কিংবা শুধু অফিস চালানোর একটি বিভাগ নয়। মানুষকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি উৎপাদন ব্যবস্থার আখের-কল চলতে থাকে, তাহলে আত্মহত্যার অতিমারী অনস্বীকার্য। একদা শ্রমজীবী মানুষদের নিজের অবস্থা পর্যালোচনার একশো প্রশ্নের প্রশ্নাবলি তৈরি করে দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। আর কেউ না বুঝুক, অন্তত একজন শ্রমজীবী মানুষ নিজে বুঝবেন, আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি। হয়তো সেখান থেকেই মিলবে এই অবস্থান অতিক্রমের পথ। কিন্তু হায়! স্বর্গ-স্যারিডন-ইউনিয়ন কোনও কিছুই আর নেই বর্তমান শ্রমজীবীদের হাতে। ফলে কেবল মেনে নেওয়া আর না-মানতে পারা। ফলত জীবনের ভার অসহ হয়ে ওঠে। উটের গ্রীবার মতো নিস্তবদ্ধতা এসে দাঁড়ালে তখন আর অদ্ভুত আঁধারকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না কেউ কেউ।
অন্য আত্মহত্যার ঘটনাটি বাস্তবতার আর এক নিষ্ঠুর পরত খুলে দিয়েছে। গাজিয়াবাদে এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। চাকুরিরতা ছিলেন। স্বামী চিকিৎসক। অথচ বিবাহিত জীবনে নিজেকে গৃহ-সহায়িকার বেশি আর কিছু ভাবতে পারেননি তিনি। সেই ব্যবহারই তিনি পেয়েছেন। অতএব নিজের জন্য এই মর্যাদা বরাদ্দ করেই এই পৃথিবীর যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, অপমান থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছেন তিনি। এই ঘটনা যেন শিক্ষিত সমাজের আত্মছলনা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। এ-সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতা যে নতুন মুখোশ পরে নিয়েছে, তাতে একে সাধারণ ভাবে চেনা মুশকিল। পুরনো গোঁড়ামি ছেড়ে সে আর নারীকে শিক্ষায়, চাকরিতে বাধা দেয় না। পোশাকের স্বাধীনতা, কথার স্বাধীনতার মতো ধারণাগুলো এই পরিসরে দিব্যি ঘোরাফেরা করে। অতএব বাইরে প্রগতির ঝাঁ-চকচকে সাতমহলা। অন্দরে এখনও সেই তাচ্ছিল্য, লাঞ্ছনার ঊর্ণা। এই বাস্তবতা এ-সমাজের নির্মিত। যেখানে একই সঙ্গে একটি মেয়েকে হতে হবে চাকুরিরতা ও গৃহকর্মে সুনিপুণা। অতীতের টেমপ্লেট ছেড়ে এসে পিতৃতন্ত্রের এই নতুন বয়ানের সঙ্গে অহরহ ঝুঝতে হয় আজকের মেয়েদের। চাকরি তাঁরা করবেন ঠিকই। তবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন পরিবারকেই। এ সমাজের এমনটাই কামনা। সেই কামনা পূরণ করতে করতে ক্লান্ত এই তরুণী যেন জানিয়ে দিয়ে গেলেন, চলে যাওয়াও আসলে একরকম প্রতিরোধ। প্রতিরোধ। যা অন্যকে জানিয়ে দেবে, এই ছলনায় পা না দিতে।
দুটি আত্মহত্যাই এই সমাজের তথাকথির সভ্যতার মুখ আর মুখোশকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিয়েছে। এমন নয় যে, অনেকে অর্থহীনতার ভার বহন করছেন বলেই তা ঠিক বা কাম্য। যে বাস্তবতা দুজন সহ-নাগরিককে এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে দিল, তা মানুষকে বিপন্ন করে সামগ্রিক ভাবেই। সোশ্যাল মিডিয়ার দুদিনের আলোচনায় যদি তা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে আরও অনেকেই ক্লান্ত হয়ে উঠবেন ভবিষ্যতে। জীবনের স্বার্থেই মানুষের বোধহয় তার আর একটু জীবন-অনুরাগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তা অর্থহীনতা আঁকড়ে ধরে নয়। বরং সেই আবর্জনা পরিষ্কার করতে করতেই এগিয়ে যাও।
একেবারে কি সবটা দূর হবে? হয়তো নয়। যে-পাথর ঠেলে একটু উপরে তোলা যায়, আবার কোন নিয়তি-নির্দিষ্ট হয়ে তা যেন গড়িয়ে নিচেই নেমে আসা। তবু সেই এক-মুহূর্তের থামা। পুনরায় উপরে তোলা।
ওই এক লহমাতেই জীবন সিসিফাস। তার কি আর হেরে গেলে চলে!