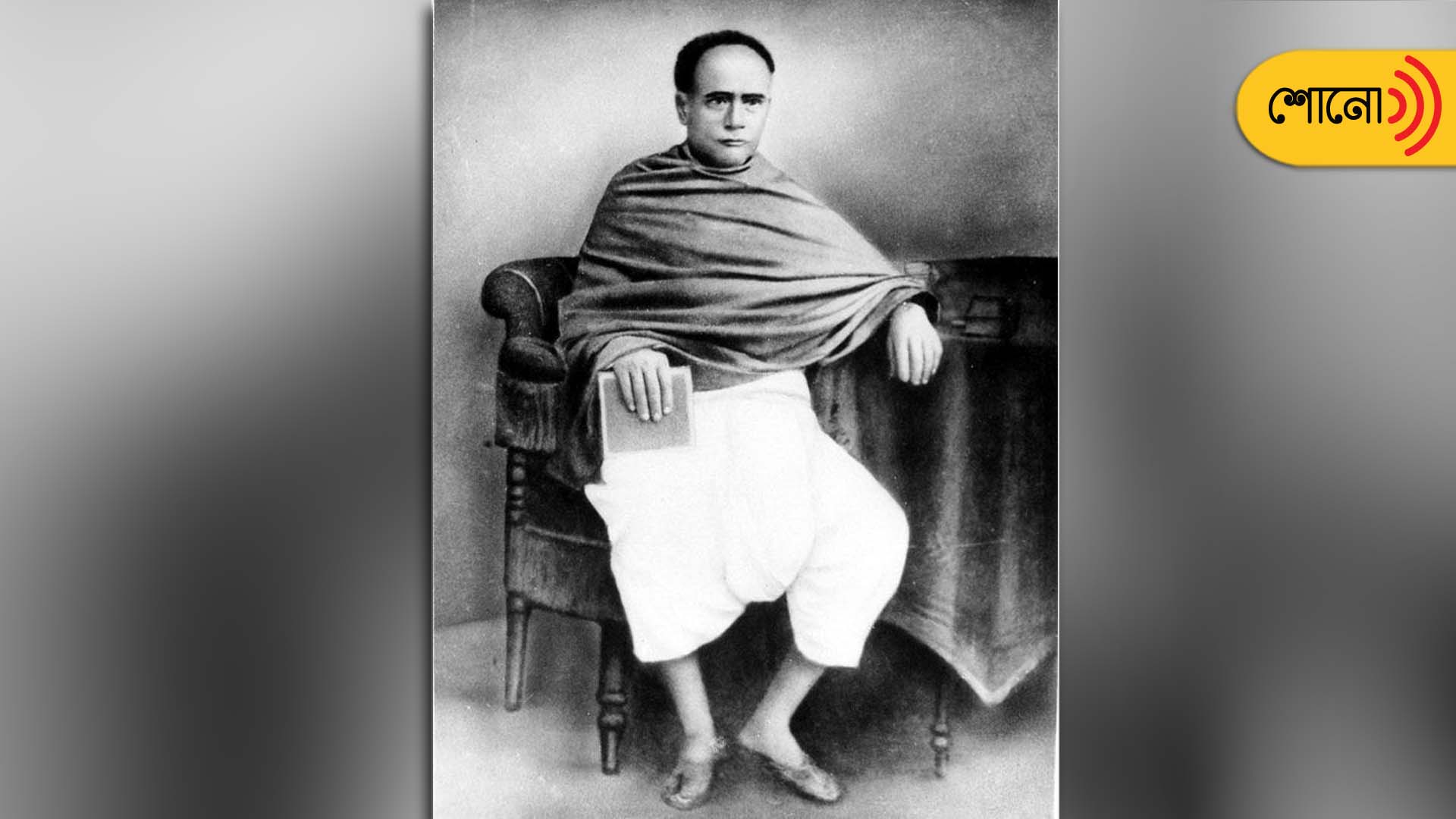পয়লা-Podcast: পয়লা বৈশাখ যদি অঘ্রানে হত, কী ভালোই না হত… । পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: April 14, 2025 7:42 pm
- Updated: April 14, 2025 9:20 pm


বাঙালির পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখের বাঙালি। ঠিক আগের মতোই আছে! নাকি পয়লা বৈশাখ নেহাত পোশাকি উদযাপনে এসে ঠেকেছে? তা নিয়েই নিজের ভাবনা জানালেন, পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
পড়ে শোনালেন: চৈতালী বক্সী। অলংকরণ: দীপঙ্কর ভৌমিক।
পয়লা বৈশাখ নিয়ে আমার একটা দুঃখ বরাবর রয়ে গেল। পয়লা বৈশাখটা ওই পৌষ-অঘ্রান নাগাদ পড়লে কী ভালোই না হত! নতুন জামা পরে গলদঘর্ম হয়ে হালখাতার দোকানে ঠান্ডা রঙিন শরবতের গ্লাসের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকতে হত না। যতই বাঙালি আজ কর্পোরেট হয়ে হাফপ্যান্ট পরে ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম করুক, যতই মা কালী-সারদা-রামকৃষ্ণের ইনোভেটিভ ক্যালেন্ডারের মায়া কাটিয়ে, অনলাইন গুপ্তপ্রেস লুপ্তপ্রেস তিথি ধরে নেক্সট দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন করুক, গরম বৈশাখের দুঃখ অস্বীকার করতে পারে এমন বাঙালি খুঁজে আনুন দেখি!
অথচ পয়লা বৈশাখটা এককালে সেই খাস নভেম্বরেই পড়ত, ঠিক যেমন দুর্গাপুজো আগে বসন্তকালে হত। অঘ্রানের মিঠে ধান ওঠার সিজনেই নতুন বছর ধরা হত তখন। নতুন বছর মানে তো পুরনো বছরের ট্যাক্স দিয়ে সব হিসেব মিটিয়ে নতুন শুরু। এই আকবর স্যার বারোভূঁইয়াদের সবক শেখানোর চক্করে ট্যাক্সের টাইমটা পালটে করে দিলেন খটখটে বৈশাখে। এই জন্যই সেলিম-আনারকলির প্রেমটা আর হয়ে উঠল না, এত খিটখিটে বেরসিক শ্বশুর হলে কী আর হবে! খেজুরগুড় পিঠে-পুলির বদলে আমপান্না, যত হাসি তত কান্না। আকবর স্যার বললেন, ‘পয়লা বৈশাখ মে হি তুমলোগ লগান দেগা। খাতা কা হাল নগদ করেগা।’ এত খারাপ হিন্দি বলেননি ধরে নিলেও এই থেকেই হালখাতা টার্মটা এসেছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। অথচ বাঙালি কি এতে মোগল হয়ে গেল? ধুর মশাই! এত কিলো ডালডার মোগলাই খেয়েও যখন বাঙালি বাঙালি-ই থেকে গিয়েছে, তখন এ প্রশ্ন অবান্তর। হালখাতা ফারসি হলেও বাঙালির। ঠিক যেমন হাল আর খাতা বাংলা নয় বললে বাঙালি তেড়ে আসবে, বাজার গরম হবে, সারা শহর বরফ আনতে ছুটবে… আরে আরে, এগুলো তো ফারসি শব্দ সব! তাজ্জব ব্যাপার না? বাংলায় যে-ই আসে সে-ই থেকে যায়, এক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাদে।
‘আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে— অন্ধকারে জমিদারদের চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে’
– সে কবি যতই বলুন, চড়কের গাছটাই কতদিন বাঁচবে বলা যাচ্ছে না, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা কর্পোরেটের হাত ধরে এসে ফের জাঁকিয়ে বসতেই পারে। ‘হরগৌরী প্রাণনাথ, মাথার উপর জগন্নাথ, এইবার উদ্ধার কর শিব-শিব-শিব হে’ – বলে হাঁক পাড়া গ্রাম্য হলেও ইনস্টাগ্রাম্য নয় বিশেষ। চড়ক গাজন এখন আউট অফ ফ্যাশন হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শিবের বিয়ের আগে ব্যাচেলর পার্টি বাবদ ভয়ানক সব কেরামতি, সঙ্গে গাজনের গান, সন্ন্যাসীদের সাজসাজ রব। শিবের বরযাত্রী বলে কথা! বাঙালি এখন প্রি-ওয়েডিং শুট করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। জলে-স্থলে-সোশ্যাল মিডিয়াতে ‘সঙ্গীত’ না করে বিয়েতে ঢোকে না। বিয়ে মানেই যে কাটাঝাঁপ আগুনঝাঁপ তা আমরা কি ভুলেছি? নাকি বিয়ে মানেই আগে ভূতের নেত্য তা কেউ ভুলতে পেরেছি? বাঙালি পোশাক বদলাতে ভালোবাসে। কাল আমরা চাইতাম ‘এক পীরিতে শিব শ্মশানবাসী’, আজ চাইছি ‘লায়লা দেবে মজনুকে শশা’। সে গান কি লোকের গান? লোকেই জানে। কাল কী চাইব, আদৌ কাল থাকব কি-না, সে প্রশ্ন কিঞ্চিৎ দার্শনিক।
ধুতি-শাড়ি থেকে পাতলুন হয়ে লুঙ্গি -গামছা-নাইটির যুগ পেরিয়ে বাঙালি শহুরে উচ্চবিত্তে শর্টস ইউনিসেক্স যখন হয়ে উঠতে পেরেছে, লোকগানের ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রোডাকশন ছেড়ে কর্পোরেট হাউসের বানানো খিচুড়ি ভাষার গানে ক্রমশ ঘেঁষে যেতে পেরেছে, তখন আগামীর চাওয়াপাওয়াগুলো নিতান্তই আপেক্ষিক হয়ে ওঠে না! আমরা বাঙালি, বদলে যেতে ভালোবাসি, আবার বদল নিয়ে হা হুতাশ করতেও ভালোবাসি। এই আত্মবিরোধের জন্য আমরা বিখ্যাত। যা পাই তাই জিভে দিই, সে ভাষা হোক, কী খাদ্যবস্তু! মাঝখান থেকে চিল্লি চিকেন হোক কি বিরিয়ানি, মোমো হোক কি থুকপা, বাঙালির জিভে উতরে গেলে খবর এবং খাবার দুই-ই বাঙালি হয়ে যায়। সেই যে বাঙালি সদ্য মডার্ন কৌলীন্য শিখতে গিয়েছিল অবাঙালি পণ্ডিতের কাছে, নিরামিষ খাবার বিধান-টিধান শুনে এসে বেমালুম মাছের ঝোলে কুমড়ো বেগুন দিয়ে নিরামিষ মাছ বানানোর নব্য শাস্ত্র লিখে ফেলল, সে ঐতিহ্যেরও নয় নয় করে আট-ন’শো বছর হয়েই এল। নষ্ট্রাদামুস অবধি জানতেন না বাঙালির জিভ এমন ‘জো জিতা ওহি সিকান্দার’ খেলবে, চিন জাপান হনলুলু আমেরিকা কিচ্ছু রেয়াত করবে না। গঙ্গা যমুনার দেশের লোক আমরা, খিদে যে আমরা বিলক্ষণ চিনি।
এই পয়লা বৈশাখ সকাল হতেই এস্থেটিক পান্তাভাতের ইন্সটাগ্রাম্য ছবির দিকে তাকিয়ে উঁচু-নিচু সব বিত্তেই কিঞ্চিৎ নালঝোল সুড়ুৎ করে টেনে নেব না আমরা? নইলে আমাদের পেটের, জিভের কাছে ঋণ হাল নাগাদ হয় না বটে। হালখাতাই হোক কি হুজুগ, পোশাক হোক কি ড্রেস-আপ, জিভে যতদিন সরস্বতী আছেন, খোদার কসম বলতেই হবে, কিছু মায়া রয়ে গেল।