
পয়লা-Podcast: পয়লা বৈশাখ এখন সত্যিই যেন একটা পণ্য । সুমেধা চট্টোপাধ্যায়
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: April 14, 2025 5:13 pm
- Updated: April 14, 2025 9:23 pm

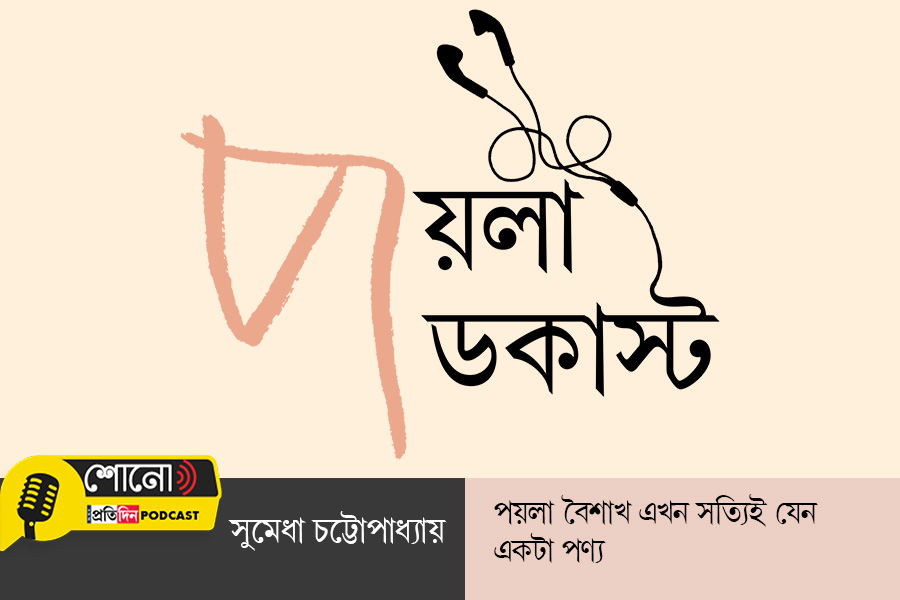
বাঙালির পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখের বাঙালি। ঠিক আগের মতোই আছে! নাকি পয়লা বৈশাখ নেহাত পোশাকি উদযাপনে এসে ঠেকেছে? তা নিয়েই নিজের ভাবনা জানালেন, সুমেধা চট্টোপাধ্যায়।
পড়ে শোনালেন: চৈতালী বক্সী। গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক।
আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে স্কুলে পড়াকালীন প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে আমার নাচের স্কুল ‘মন্দ্র’-র সৌজন্যে যোগ দিতাম শিশু-উৎসবের নাচের অনুষ্ঠানে। ‘নিখিল বঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদ’ তা পরিচালনা করত। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। তখন গাড়ি ছিল বিলাসিতা। নাচের শেষে, ‘ড্রেস’ অক্ষুণ্ণ রেখে এবং মেক-আপ না তুলে ফিরতি পথে মায়ের সঙ্গে হালখাতা করতে যেতাম আমাদের শহরতলির ছোট ছোট কয়েকটি দোকানে। বাংলা যে ক্যালেন্ডারটির প্রাপ্তি ঘটত – যেখানে থাকত ঠাকুরের ছবি – ওটা আমার ঠাকুমার খুব প্রিয় ছিল। ঝুলিয়ে দেওয়া হত তাঁর ঘরে। তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল প্লাস্টিকের গ্লাসে দেওয়া কমলা কোল্ড ড্রিংক। প্রায় ‘গরম’ হয়ে যাওয়া, ঝাঁজবিহীন এই শরবত আমার কাছে পয়লা বৈশাখের বাঙালিয়ানার প্রতিভূ ছিল আমার ছোটবেলায়।
দিন বদলে গেল। কালের প্রকোপে এখন আর শিশু-উৎসব হয় না। সেই জায়গা নিয়েছে ঝাঁ চকচকে সামার ক্যাম্প। হালখাতার পুজো হয় ঠিকই, কিন্তু আমরা এখন শহরতলি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতাবাসী। তাই সেই বাঙালি দোকানগুলো এখন ঠিক কতটা ‘গরম’ কোল্ড ড্রিংক দেয়, জানা নেই। পয়লা বৈশাখ এখন সত্যিই একটা পণ্যে পরিণত। বেশিরভাগ ‘বাঙালি’ চেষ্টা করে ওই এক দিনে প্রকৃত বাঙালি ‘সাজতে’। এ ভাবনা সঙ্গত, কেননা চারিদিকে কেবলই দৃশ্য়ের জন্ম! পয়লা বৈশাখে সাবেকি শাড়ির দোকানে ধুন্ধুমার সেল, বাঙালি রেস্তরাঁ এবং গজিয়ে ওঠা ‘মারাত্মক ভালো’ সব ক্লাউড কিচেনে ‘ঠাকুমার হারিয়ে যাওয়া রান্না’র হরেক এক্সপেরিমেন্টের বহর। যে-বাড়ির ছেলে বা মেয়ে সারাবছর বাংলা পড়েই না, কোনওরকমে পাস মার্ক ওঠে, সেও কিনা সেদিন বাংলা কবিতা আওড়াতে বসে। সবচেয়ে মজার বিষয়, পয়লা বৈশাখের দিন নন্দন-আকাদেমিতে ‘চিল আউট’ করতে আসা সাবেকি সাজের কপোত-কপোতীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘বাংলায় কোন সন এল?’ তাহলে তারা পালানোর পথ পায় না। আমার সামনে একবার এই ঘটনা ঘটায় খুবই অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। সারা বছর যে বাঙালিরা তাদের বাঙালিত্ব নিয়ে খুব ‘লজ্জা’ বোধ করে, এমনকি কর্মক্ষেত্রে বিদেশি ক্লায়েন্টের সামনে নিজের পরিচিতি দিতে গিয়ে বাংলা মিডিয়াম স্কুলের নামও উচ্চারণে দ্বিধা বোধ করে, তারাও দেখি বড় মুখ করে পয়লা বৈশাখের দিন ‘চিতল মাছের মুইঠ্যা’ খুঁজে বেড়ায়। এটাই এখন ‘ট্রেন্ডিং’, তাই এটা মেনে নেওয়াই ভালো, নয়তো শুধু মন খারাপ হবে।
তবে পরিস্থিতির সবটাই মন্দ নয়। কিছুটা ভালোও আছে। কলকাতার আশেপাশের অনেক রিসর্ট বা হোমস্টে এইদিন অনেক নামী শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, অবশ্যই বাংলা গানের। আমি একটি হোমস্টের কথা জানি, যারা সারা বছরই উঠতি লোকশিল্পী এবং গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে গিয়ে বাংলা গানের অনুষ্ঠান করে থাকেন। সারা বছরই চলে বাঙালিত্বযাপন। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় আগে এই দিনে বসত এক মিলনমেলা। দে’জ বা আনন্দ-র অফিসে গেলেই আলাপ হয়ে যেত নামী লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে। আজও এই ধারা বিদ্যমান। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ছাড়াও, বছরভর নানা ছোট-ছোট বইমেলা, বইবাজার, সাহিত্য উৎসবের মাধ্যমে বাঙালিয়ানাকে ধরে রাখার চেষ্টাও চলে। আরও আছে। আকাশবাণী বা ডিডি বাংলা অনেকদিন ধরেই ত্যাজ্য ছিল। নানা বাংলা অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার, সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে বাঙালির জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই দুটি ‘প্রাণ’, কয়েকজন সৎ বাঙালির উদ্যোগেই আবার ফিরে এসেছে।
বেশ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগপতি মহিলা শাড়ি এবং নানান ধরণের এথনিক জামা-কাপড়ের ব্যবসায় নেমেছেন। নিজস্ব ব্র্যান্ডিং করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পরিধানের বাঙালিয়ানায় জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ শাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি কিংবা লেস দেওয়া ঘটি হাতা ব্লাউজ। এগুলো তাঁরা সারা বছরই বানান, শুধুমাত্র ‘বোশেখি’ বাঙালি সজানোর জন্য তাঁদের এ কর্মকাণ্ড নয়। আমার একজন এক্স-কলিগ আমেরিকায় সেটল করেও ‘বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ম্যারিকা’ পুত্রকে সুন্দর বাংলা কবিতা শেখান, সারা বছরই ওদের সাজে বাঙালিয়ানা লেগে থাকে। সেই ছেলে গুরুজনকে প্রণাম করতেও জানে। তাকে সেই শিক্ষা তার প্রবাসী বাঙালি মা-বাবাই দিয়েছে।
তাই আমার মতে, ধুতি-পাঞ্জাবি, ক্যালেন্ডার, হালখাতা, মিষ্টি সব শুধু বৈশাখে হয়, বাকি সময়ে ‘মৃতপ্রায়’- এটা পুরোপুরি সত্যি নয়। বড় কথা হল, সারাবছর আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে আমরা চাই কি-না; আমাদের আদৌ ইচ্ছা আছে কি-না এই ক্ষেত্রে; ইচ্ছা থাকলেই উপায় হবে, নয়তো শত চেষ্টাতেও ‘বোশেখি বাঙালি ‘ সারাবছর ‘এন্ডেঞ্জারড স্পিসিস’ হিসেবেই থেকে যাবে।











