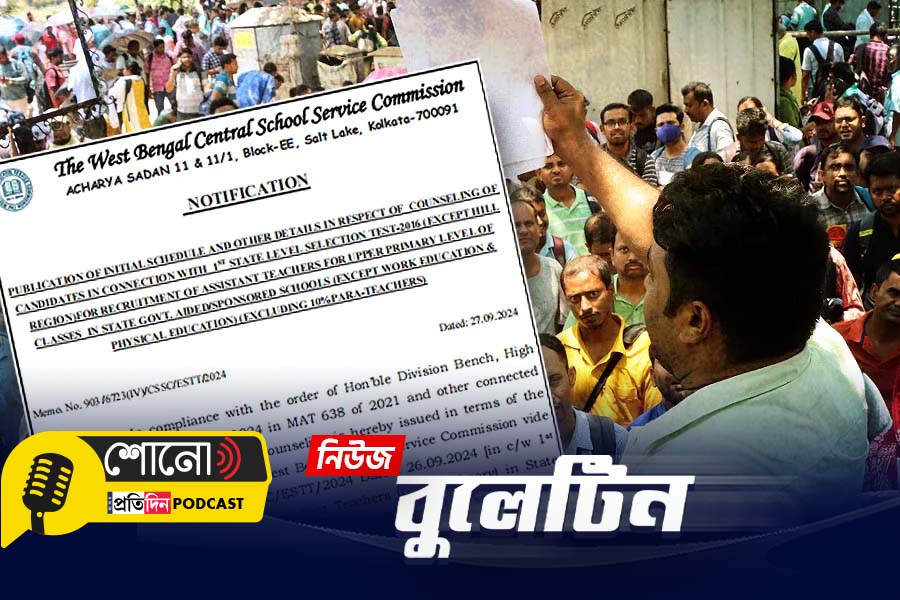পয়লা-Podcast: বাঙালি সত্তা কি কেবল ধুতি-পাঞ্জাবি আর শাড়ির ভাঁজে যত্নে তোলা!। আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: April 14, 2025 8:06 pm
- Updated: April 14, 2025 9:14 pm

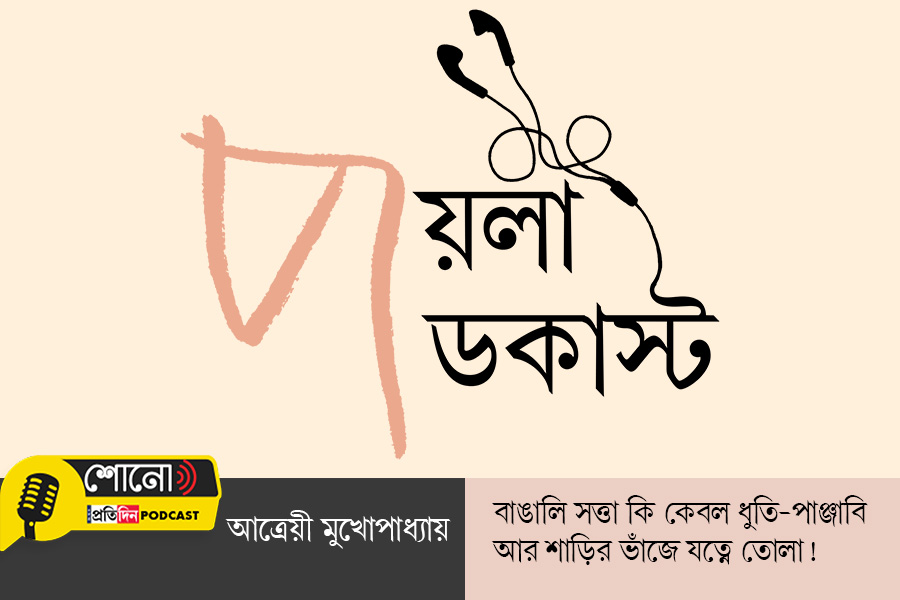
বাঙালির পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখের বাঙালি। ঠিক আগের মতোই আছে! নাকি পয়লা বৈশাখ নেহাত পোশাকি উদযাপনে এসে ঠেকেছে? তা নিয়েই নিজের ভাবনা জানালেন, আত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়।
পড়ে শোনালেন: চৈতালী বক্সী। গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক।
রবীন্দ্রমথিত উত্তর-আধুনিক বাঙালি মননে খোদাই করা পয়লা বৈশাখের সাংস্কৃতিক উদযাপনের ইতিহাস, বাস্তবিক অর্থেই অরাজকতার বিরুদ্ধতার ইতিহাস। ১৯৬৭-তে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার ওপরে, পাকিস্তানি ভাষা-সন্ত্রাসী ফতোয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে পয়লা বৈশাখ-কে সাহিত্য ও শিল্পচর্চার উৎসবে পরিণত করলেন। অর্থাৎ, এই বৈশাখ মাসের ১ তারিখে, মা লক্ষী ও মা সরস্বতী একসঙ্গে বাঙালির ঘরে, বাঙালির মনে জায়গা করে নিলেন।
কেবল একটি দিন নতুন জামাকাপড় পরে বাংলায় গান গাইবার জন্য এই প্রতিবাদ ছিল না। বরং সচেতনভাবে ধর্মীয় সত্তার ঊর্ধ্বে উঠে বাঙালি জাতিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখব প্রত্যয়ী সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে- এই সহজ সত্যি সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। যে কোনও আনন্দউৎসবে খাওয়া-দাওয়া গৌণ করে রাখা বাঙালির ‘ধর্ম’ নয়। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে পান্তাভাত খুবই সহজলভ্য একটি খাবার এবং তার সঙ্গে ইলিশ তাদের জাতীয় মাছ; ফলে এই খাবারের আয়োজনে খুব বেশি ঝামেলা-ঝক্কি নেই। তাই পান্তা-ইলিশ বাংলাদেশের মানুষের কাছে নববর্ষ উদযাপনের একটি ঐতিহ্য বহনকারী খাবার।
আমি জানি না, বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ মাছ-ভাত বাদ দিয়ে কতটা বাঙালি? কিন্তু আমরা এদেশীয় বাঙালিরা বেশ কিছুক্ষেত্রে পোশাকি বাঙালি হয়ে উঠেছি তো বটেই। বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার দৌড়ে আমরা বাংলা ভাষা বাদ দিয়ে জার্মান, ফরাসি, চাইনিজ ভাষা শিখি আর ইংরিজি তো আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আমরা ‘হারবার্ট’-এর ইংরিজি অনুবাদ পড়ি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জাপানি হয়ে জন্মালে মুরাকামির সঙ্গেই তাঁকে একেবারে পড়তে পারার সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ি এবং প্রতিজ্ঞা করি, বিনয় মজুমদার ফরাসিতে অনূদিত হলে নিশ্চিতভাবেই তা পড়ে ফেলব। জাঁ পল সার্ত্রে খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে আমাদের ‘বিবমিষা’-র মানে বুঝিয়ে যান, অথচ লীলা মজুমদার নেহাত খেলাচ্ছলেও ‘উনপাঁজুরে’ শব্দের অর্থ শেখাতে ব্যর্থ হন। আমাদের অনায়াস ‘দারিদ্রতা’, ‘সরলতা’, ‘সখ্যতা’, ‘দারিদ্র্য’ ও ‘সারল্য’-র প্রতি ‘সখ্য’ জন্মাতে দেয় না।
তবে এই সমস্যা বোধ করি আজকের নয়। ১২০২ বঙ্গাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-তে লিখছেন- ‘ইংলিশ ম্যান, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েচে। হরিণ মাংসের মত কোনো কোনো বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসী না হলে গ্রাহকরা পান না – ইংরিজি কাগজ সেরকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক।’ অর্থাৎ আমরা বাঙালিরা নিজে থেকে ইচ্ছে করেই হোক কিংবা বৈদেশিক ঔপনিবেশিকতার ছায়ামুক্ত হতে না-পেরেই হোক, আমাদের সত্তাকে কেবল খাদির ধুতি-পাঞ্জাবি আর হ্যান্ডলুমের শাড়ির ভাঁজে যত্ন করে তুলে রেখেছি। বছরে তিনবার নববর্ষ, রবীন্দ্র-জয়ন্তী ও দুর্গাপুজোয় সেই অসহায় সত্তাকে জনসমক্ষে নিয়ে আসি, আদর করে সাড়ম্বরে দামি দামি ‘বাঙালি কুইজিন’ খাওয়াই, বাংলায় গান গাওয়াই, উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করাই, এবং দিনের শেষে ‘মায়ার খেলা’-য় নৃত্য পরিবেশন করিয়ে ঘুমি পাড়িয়ে দিই।
একটি ভাষা আমার মায়ের ভাষা বলে সেই ভাষার আপাদমস্তক সব জেনে ফেলতে হবে এমন ভীষ্মসুলভ পণ সম্ভবত মহাকাব্যেই নেওয়া সম্ভব, বাস্তব পৃথিবীতে নয়; এবং সেই ভাষা ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় কোনও ভাষা শিখব না, এমন কূপমণ্ডূক মানসিকতাও প্রশ্রয়যোগ্য নয়। কিন্তু তাকে অপমানে, অনাদরে, অপাংক্তেয় করে রাখতে হবে- এটাও কি আমাদের জাতিচেতনার অপমান নয়? বাংলা ভাষা কোনও ‘কুলিন’ ভাষা নয়, কোনওদিন ছিলও না। বিবিধ জাতি, ধর্ম, বর্ণের কাছে সে ঋণী। এবং এখানেই তার মহত্ত্ব। বাংলা মানুষের ভাষা, তার সংস্কৃতিও মানুষের সংস্কৃতি, সহজিয়া সংস্কৃতি। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ’ প্রবন্ধে লেখার ওজন সম্পর্কে তুলনা টেনে লিখছেন, ‘বালা, গালা ভারা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই’। অর্থাৎ, ‘আমাদের অফিসে ১ সপ্তাহ ধরে ‘শাওয়ান সেলিব্রেট’ হবে না বলে, সহজভাবে বলতে পারি ‘শ্রাবণ মাস উপলক্ষে অনুষ্ঠান হবে’।
ফলে রাবীন্দ্রিক সাজগোজের পাশাপাশি সেই সহজিয়া ভাব, যা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে ঋদ্ধ করেছে তা যদি উপলব্ধি করতে পারতাম, তাহলে হয়তো সম্পৃক্তভাবে বাঙালি হয়েই বাঁচতে পারতাম আমরা।