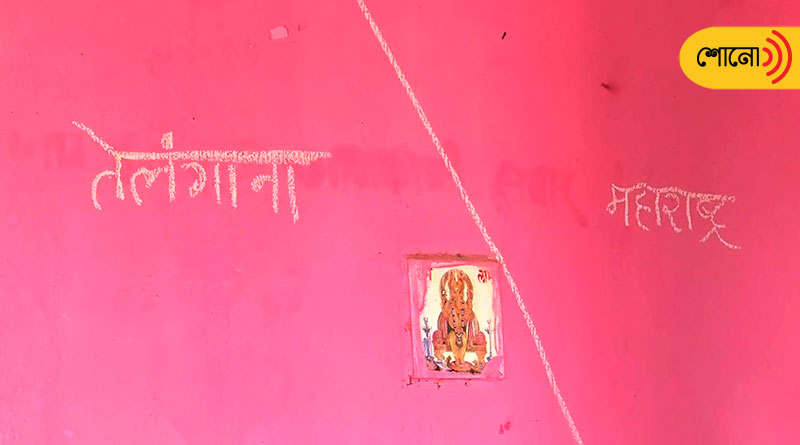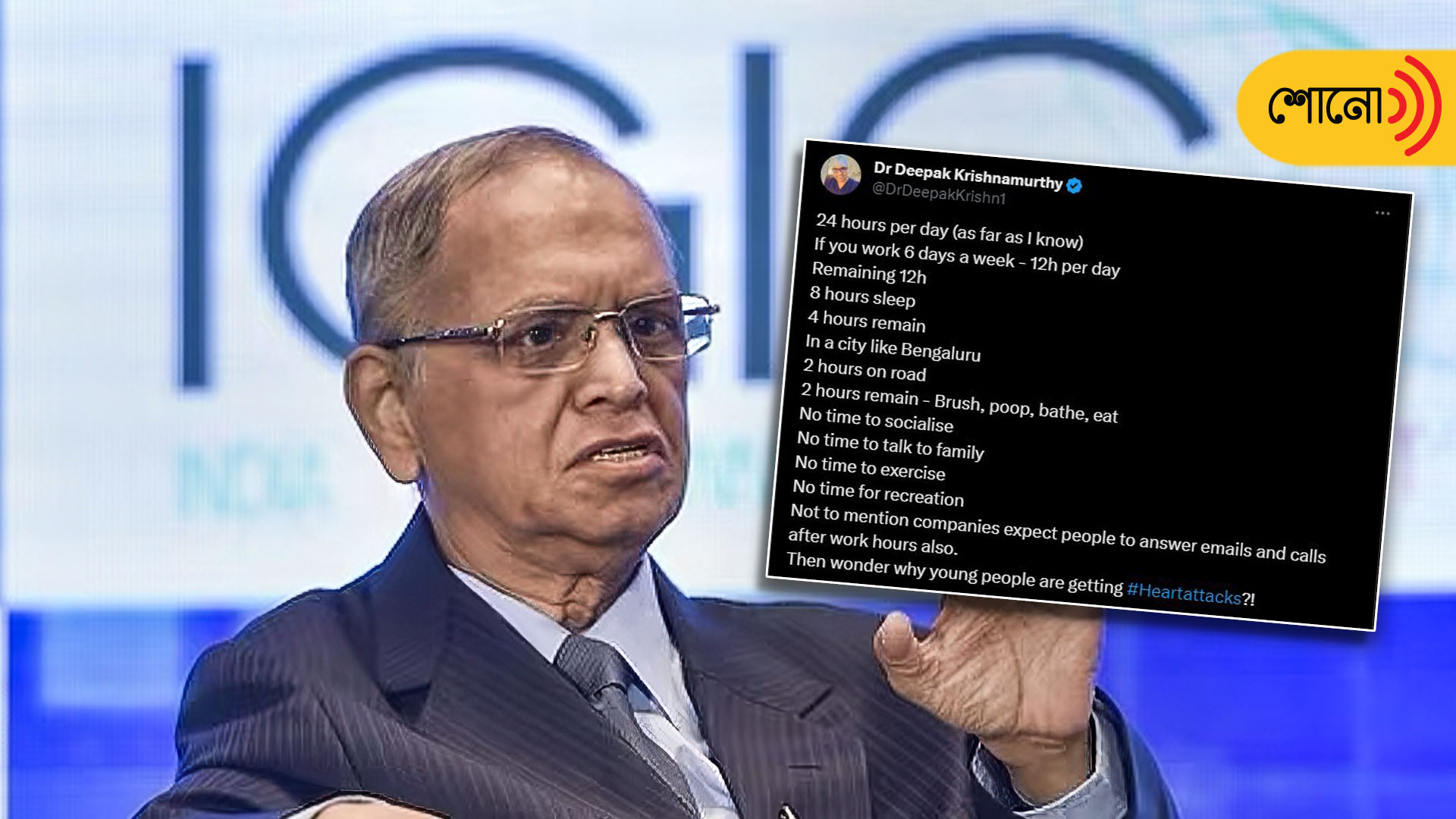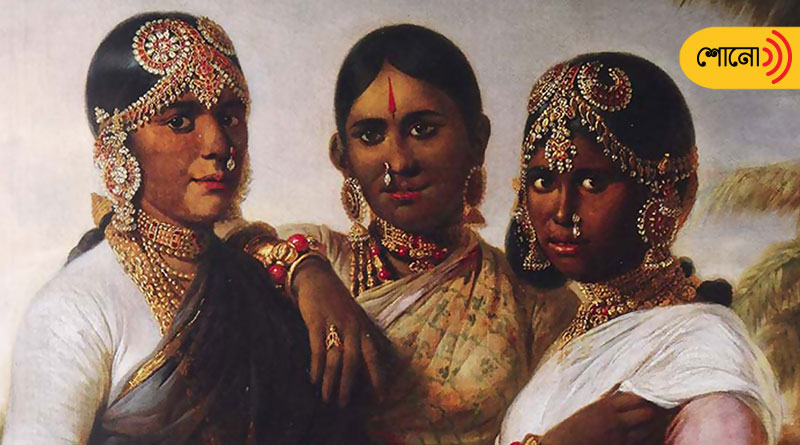পয়লা বৈশাখ, বাঙালির রসনা-যাপনের ফার্স্ট চ্যাপ্টার
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: April 13, 2025 8:40 pm
- Updated: April 14, 2025 2:22 pm


বাঙালি এত কিছু হারিয়েছে, তবু নিঃস্ব হয়ে যায়নি। তাই আজও পয়লা পড়লে ভরদুপুরে ঠাকুরঘরে শাঁখ বাজে। একান্নবর্তীর টেবিলে পাত পেড়ে চোদ্দগন্ডা। মাছ-ভাতের সঙ্গে মিশে যায় খুশির হিল্লোল। ভেসে থাকে বেঁধে বেঁধে থাকার সুঘ্রাণ। বাঙালির সেই রসনাতৃপ্তির বিবরণ দিলেন সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়।
বিদঘুটে কাণ্ড মশাই! সেদিন দিল্লি থেকে এক তুতো-দাদা ফোন করেছিল। করে যা বলল, তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম! শুনলাম, দিল্লিতে নাকি দর্জির দোকানে লম্বা লাইন। তা পড়তেই পারে। দুর্গাপুজোর সময় পাড়ার সনাতন দর্জিকে দেখেছি, রাতদিন এক করে মেশিন চালাতে। একবেলা খেতো। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কষ্ট হয় না? সে-কথা শুনে তার কী হাসি! কুমড়োর বিচির মতো দাঁত বার করে বলেছিল, ‘ধুস, এখন না খাটলে সারা বচ্ছর খাবো কী?’
দিল্লির দর্জিদের এখন সেই সনাতনের দশা। কিন্তু বিটকেল কাণ্ডটা কী হয়েছে, জানেন? সেই লম্বা লাইনে একটাও মানুষ নেই! তাহলে? শুনলাম, দিল্লির আনাচে-কানাচে যত হুমদো বিড়াল, মেনি থেকে দামড়া হুলো- তারা নাকি গুঁতোগুঁতি করে লাইন দিয়েছে দর্জির দোকানের সামনে! কারণ শুনলে পিলে চমকে যাবে। দিল্লির কোন বেপাড়ায় নাকি মাছ খাওয়া নিয়ে ব্যাপক ক্যাচাল। কয়েকজন রামচন্দ্রের নামে দিব্যি কেটে বলে গেছে, এ পাড়ায় থাকতে গেলে মাছ খাওয়া বন্ধ করতে হবে। সিধে কথায় কাজ হলে ভালো, নয়তো দুধের দাঁত উপড়ে নেবে। হক কথা। যস্মিন দেশে যদাচার। তাছাড়া তুতো–দাদা বলল, জায়গাটা নাকি চিত্তরঞ্জন না মনোরঞ্জন পার্কে। তা পার্কে যাবি যখন যা, গিয়ে প্রেম-পিরিতি কর। মাছের ছোঁয়া-নাড়া করার কি দরকার! গায়ে আঁশটে গন্ধ নিয়ে পার্কে ঘুরে বেড়ানো কোন কালের ভদ্রতা বাপু?
কিন্তু বিড়াল। ওরা পড়েছে ফাঁপড়ে। জীবনধারণ করতে গেলে তো শুধু লিক্যুইডে হয় না, সলিডও লাগে। দুধ বেশি খেলে পেট ফাঁপবে। মাছসমেত ধরা পড়লে আরেক কেলো। অতএব চোরাকারবার। সেই উদ্দেশ্যে দর্জির দোকানে ক্যাট-ওয়াক চলছে। শুনলাম, মার্জারকুলের দাবি একটাই। বডির সঙ্গে মানানসই একটা চোরা-পকেট বানিয়ে দিতে হবে। যাতে মাছের কাঁটা সজারুর মতো বেরিয়ে না পড়ে। বমালসমেত ধরা পড়লে যে কপালে দুঃখ আছে। দাঁত উপড়ে নেবে! ফোকলামুখো দেখতে ঠিক কেমন লাগবে, ভাবতেই মনে পড়ে গেল রাঘব কাকার কথা। না, রাঘব কাকার বত্রিশ পাটিই আছে। সমস্যা অন্যজনকে নিয়ে।
গতবার পয়লা বৈশাখে রাঘব কাকার বাড়িতে এনআরআই জামাই এসেছিল। দুপুরে এলাহি আয়োজন। দু’-তিন রকমের মাছ, কচি পাঁঠার ঝোল। শেষপাতে লাল দই। বাঙালির বারো মাসে তেরো। রাঘব কাকারও তাই। রাজাবাজারে পেরেকের ব্যবসা। কাঁচা টাকা। পুজো-পার্বণ, উৎসবে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাবে, সেটাই তো বাঙালিয়ানা। দুপুরের ইনিংস ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল। জামাই বড়ি-পোস্ত ছিটানো লাল শাক আর এক বাটি নবরত্ন ডাল সাপটে সবে চিতোলের পেটির দিকে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় বিপত্তি। অনামুখো বিড়াল চোখের নিমেষে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল চিতোল, এক্কেরে ‘বাজ-বাহাদুর’ কায়দায়। ঘটনার আকস্মিকতায় জামাই পুরো জেলিফিশ। চেয়ার-টেবিল উল্টে একাকার কাণ্ড। থালা-ভর্তি ভাত ‘উড়ো খই গোবিন্দায় নমো’র মতো সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। খাসির দুটো পিস উড়ে গিয়ে পড়ল আলমারির মাথায়। আমের চাটনি আর এঁচোড়-চিংড়ি সাদা দেওয়ালে মিলেমিশে যাকে বলে ‘বার্জার কালার’! রাঘব কাকা ‘রং তো আচ্ছা হ্যায়’ বলবেন কী, চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন।
এমন লঙ্কা কাণ্ড চোখের সামনে দেখে মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন। রাঘব কাকার স্ত্রীর পক্ষে আরও কঠিন। তিনি কুপিত হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা জামবাটি ছুড়ে মারলেন নচ্ছার বিড়ালের দিকে। চিতোল-হাতানো বিড়ালের রিফ্লেক্স যে জন্টি রোডসের মতো হবে, জানতেন না রাঘব-গিন্নি। ফলে সুদর্শন-চক্র সম জামবাটি অচিরেই লক্ষ্যচ্যুত হল, তবে নিশানা খুঁজে নিতে দেরি করল না। সেটা সজোরে আছড়ে পড়ল চেয়ার উল্টে পড়ে থাকা জামাইয়ের হাঁ-মুখে। তাতেই কড়াৎ অ্যান্ড পড়াৎ! টুং–টুং করে খসে পড়ল জামাইয়ের সামনের পাটির দুটো দাঁত। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল। ‘রাঘববাবুর ফোকলা জামাই’ রটতে সময় লাগল না। লজ্জায়, অপমানে মুখে কাপড়চাপা দিয়ে সেই যে জামাই চলে গেল, তারপর এমুখো হয়নি। শুনলাম, এবার নাকি রাঘবকাকার বাড়ি পয়লা বৈশাখে অরন্ধন। ওইদিন রাঘবকুলে ‘ডাইন-আউট’। জামাই নাকি কোন রেস্টুরেন্টে টেবিল বুক করেছে। জাম্বো থালি নাকি খাওয়া হবে। ঘোল-সরবত তো আছেই। প্রন কাটলেট, পনির পসিন্দা, চিকেন মেইফুং-টুং কীসব নাকি আ-পদের নাম! তাতে অবশ্য ওদের বিড়ালটার কিছু যায়–আসে না।
তবে আমি কারও দোষ দেখি না। জামাইয়ের নয়, রাঘব-গিন্নির নয়, এমনকী চিতোল-হারিণী বিড়ালেরও নয়। ‘দোষ’টা আমাদের বাঙালিয়ানার! একটা কোনও মোচ্ছব লাগলেই হল। খাই-খাই শুরু হয়ে যায়। বাঙালির পার্বণ মানেই ‘খাওন-দাওন’। ষষ্ঠী পুজো থেকে ক্রিসমাস – বাঙালি সবসময় খাচ্ছে। আর পয়লা বোশেখ হলে তো কথাই নেই। ও যেন দুর্গাপুজোর ছোট ভার্সন। ফাইনালের আগে সেমিফাইনাল। আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার যেমন একটা ষান্মাসিক ছিল, ঠিক তেমনি। উৎসবমুখর বাঙালি পার্বণপ্রিয়। আরও প্রিয় তার খাওয়া-দাওয়া। ঘরোয়া অনুষ্ঠানেও তাদের ব্যস্ততা থাকে হেঁশেলঘরে। খুন্তি-হাতা, হাঁড়ি-কড়াইয়ের মেলবন্ধনে সেখানে জন্ম নেয় জিভে-জল আনা এক একটা পদ। মা-মাসি-পিসি-দিদিমা-ঠাকুর্মার সেই রন্ধন কুশলতার মূল উপকরণ কোনও বিশেষ মশলা নয়, স্রেফ আন্তরিকতা। পয়লা বৈশাখ বাঙালির সেই রসনা–যাপনের ফার্স্ট চ্যাপ্টার।
বৌদ্ধ মতে প্রথম মাস বৈশাখ, অথচ বাঙালির প্রথম মাস নাকি অগ্রহায়ণ। বাঙালি এসব ক্যারিকেচারে বিশ্বাস করে না। বরং, অন্যকে আপন করে নেওয়ার সহজাত গুণ তার বরাবর। তাই ক্যালেন্ডারে সবার প্রথমে বৈশাখ। পয়লা তারিখ পড়লেই বাঙালির নতুন বছর শুরু, নতুন বস্ত্র গায়ে চাপিয়ে। দুর্গাপুজোর শপিং-ধুম না চাপুক, চৈত্র সেলের সস্তার বারমুডা, স্যান্ডো গেঞ্জি কেনা তার চাইই চাই। আর চাই হালখাতায় নাম তোলা। হালখাতা নিমিত্তমাত্র। আসলে পুরোটাই মিষ্টির প্যাকেট আর ক্যালেন্ডার কালেকশনের ফন্দিফিকির। সঙ্গে থাকে গরমে আমপোড়া কিংবা ঠান্ডা রসনায় গলা ভেজানো। ফুল আর আলোয় সাজানো দোকানে ওই রঙবেরঙের ঠান্ডাই মূল আকর্ষণ। বাকি সব এহো বাহ্য। মিষ্টির প্যাকেট সেও রকমারি। ভিতরে শাঁসালো তালশাঁস সন্দেশ থেকে মিয়ানো খাস্তা নিমকি, পয়লা বৈশাখ মানেই মিষ্টি বহুরূপে সম্মুখে তোমার। এ মায়া কাটাবে, সাধ্য কি বাঙালির! তবে এককালে নাকি পাতপেড়ে রাধাবল্লভী-আলুর দম, পান্তুয়া চলত। তখন বাঙালির ব্যবসায় মতি ছিল। এখন সেসব মজে যাওয়া ইতিহাস। পয়লা বৈশাখ পড়লে দোকান সাজে। হালখাতায় নাম ওঠে। তবে দোকানের বাইরে ঠান্ডা কাচের বোতলে সেই রিনরিনে সুর ঘনায় না। মিষ্টির প্যাকেটও ছোট হতে হতে বোকাবাক্স। সন্দেশ, নিমকির জায়গা নিয়েছে ‘রং দে তু মোহে গেরুয়া’ লাড্ডু।
বাঙালি এত কিছু হারিয়েছে, তবু নিঃস্ব হয়ে যায়নি। তাই আজও পয়লা পড়লে ভরদুপুরে ঠাকুরঘরে শাঁখ বাজে। একান্নবর্তীর টেবিলে পাত পেড়ে চোদ্দগন্ডা। মাছ-ভাতের সঙ্গে মিশে যায় খুশির হিল্লোল। ভেসে থাকে বেঁধে বেঁধে থাকার সুঘ্রাণ। সেই খেয়ে পড়ে বাঁচার সুখে হয়তো ঢুকে পড়ে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টের ডাব-চিংড়ি, গন্ধরাজ চিকেন কিংবা ফিউশন মিষ্টি। কবি তো কবেই বলে গেছেন, ‘এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।’ সেই ভঙ্গ-বঙ্গে পরিবর্তনই শেষ কথা। সেখানে রুচি, সংস্কৃতির গিরগিটি-দশা হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে এ তো কিছু বদলায়। বদলায়নি একটা ব্যাপার। ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে ‘হালখাতা’ সেরে ফেরার সময় দেখতাম ওদের। ‘ওদের’ মানে বড় রাস্তার ধারে ফুটপাতে বসে থাকা কিছু কচি মুখ। উসকোখুসকো, অগোছালো, অনাথ। আজও তাই দেখি। বাঙালির জীবনে এত পার্বণ, ওদের জীবনে কেন একটা ‘পয়লা বৈশাখ’ আসে না!