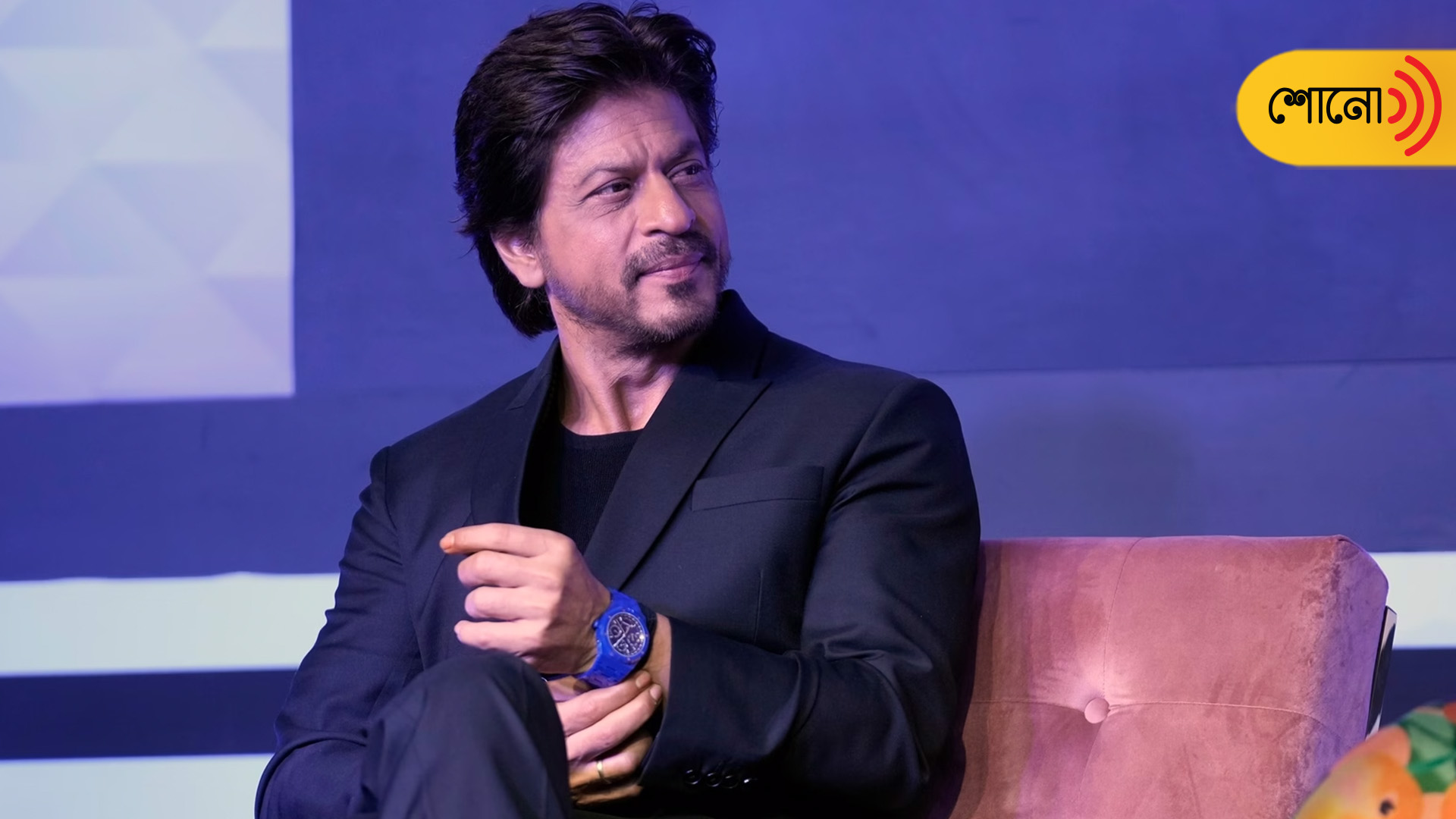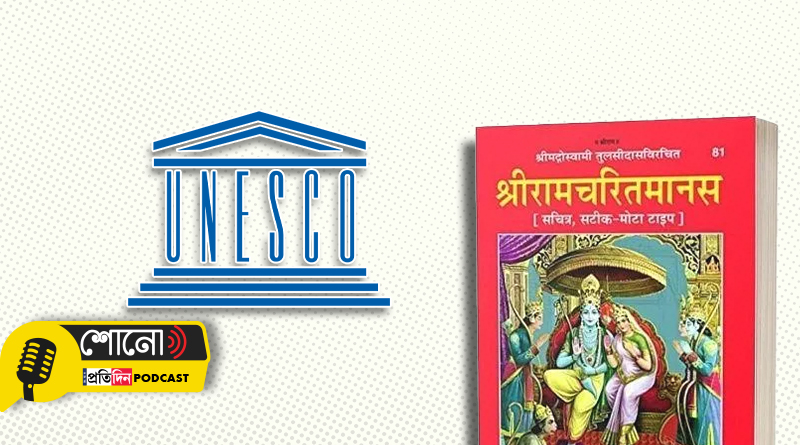মেট্রোয় সিটের কলহ গড়াল ভাইরাল করার ‘হুমকি’তে! এ কি তবে নতুন ‘থ্রেট কালচার’?
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: April 2, 2025 7:24 pm
- Updated: April 2, 2025 7:26 pm


ভাইরাল যেন ডিজিটাল-অস্ত্র। কোনও অস্ত্রের ক্ষেত্রেই বোধহয় অপব্যবহারের সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভাইরাল করার প্রবণতা কি ইন্ধন দেবে থ্রেট-কালচার?
“সিট ছেড়ে উঠবেন না তো? ভিডিও তুলে রাখলাম; ‘ভাইরাল’ করে দেব।” সম্প্রতি দিল্লি মেট্রোর ভিতর নিজের সিট এক মহিলাকে ছেড়ে না দেওয়ার কারণে এমন শাসানি শুনতে হয় এক পুরুষ যাত্রীকে। সিট বা দাঁড়ানোর জায়গা নিয়ে পারস্পরিক বিবাদ মেট্রো অথবা ট্রেনের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। নিত্যযাত্রীরা প্রায় প্রতিদিনই এসব ঘটনার সাক্ষী থাকেন। কখনও বা অংশ নেন নিজেরাই। তবে এই বিশেষ ঘটনাটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা দ্বিধাভক্ত। কেউ বলছেন, সিটটি রিজার্ভড ছিল না। অতএব, পুরুষ যাত্রীটি সিট ছেড়ে দেবেন কি-না, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁর। কেবলমাত্র কেউ মহিলা বলেই তাঁকে সিট ছেড়ে দিতে হবে, এমন দাবি করা যায় না। অন্যদিকে, বাকিদের মত, পুরুষ যাত্রীটি ঝগড়ায় না জড়িয়েও নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করতে পারতেন। তাতে বরং বাকিদের পক্ষে তাঁকে সমর্থন করা সহজ হত।
উক্ত ঘটনাটিকে সামনে রেখে প্রশ্ন উঠে আসে যে কেবল দুর্বলতর লিঙ্গ পরিচয়ের জন্যই কি ‘ভিক্টিম কার্ড’ দেখিয়ে বাড়তি সুবিধা দাবি করা যায়? সাম্প্রতিককালে দেশ ও রাজ্য জুড়ে ঘটে চলা বেশ কিছু অপরাধ সে প্রশ্নকে আরো বেশি জোরালো করে তুলছে। তবে তার থেকেও বেশি যে প্রশ্ন আমাদের ভাবায়, বা ভাবানো উচিত, তা হল ‘ভাইরাল’ শব্দটি কখন থেকে পাকাপাকিভাবে জুড়ে গেল থ্রেট কালচারের অভিধানে?
ইংরেজি ‘ভাইরাল’ শব্দটির উৎপত্তি ‘ভাইরাস’ শব্দের থেকে; ভাইরাস-ঘটিত কোনও রোগের দ্রুত সংক্রমণকে ইঙ্গিত করতেই এই শব্দের প্রাথমিক ব্যবহার। তবে নেটদুনিয়ায় এর ব্যবহার হয় তেমন কোনও ঘটনার ভিডিও বা ছবি বোঝাতে, যা নানান সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম বয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, অনেকটা দাবানলের মতো! আমরা সমান উৎসাহ নিয়ে দেখতে থাকি তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠা কোনও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির পা দিয়ে ছবি আঁকার ভিডিও, অথবা থাইল্যান্ডের বহুতল ভেঙে পড়া। পরিচিতদের পাঠিয়ে বলি, “খালি দ্যাখো! হেব্বি ভাইরাল হয়েছে!”
আমাদের হাতে ধরা মোবাইল ফোন যেন তূণ, যার ক্ষমতাধীন ‘ভাইরালাস্ত্র’ আমাদের রক্ষা করতে পারে।
তবে ছড়িয়ে পড়লেই গল্প শেষ হয়ে যায় না। বন্ধুদের তোলা নগ্ন ছবি ভাইরাল হওয়ার পর স্কুলছাত্র আত্মহত্যা করে। রূপান্তরকামী ব্যক্তি চাইলেও সমাজমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে পারে না তার রূপান্তর-পূর্ববর্তী ছবির গ্যালারি। মানুষ তাকে অতীত ভুলতে দেয় না, ইন্টারনেট তাকে অতীত ভুলতে দেয় না।
অল্প কয়েকদিন আগের ঘটনা। প্লেনে ক্রন্দনরত শিশুকে জানলার ধারের সিট না ছেড়ে দেওয়ায় শিশুটির মা ভিডিও বানিয়ে ‘ভাইরাল’ করে দেন উনত্রিশ বছরের ব্রাজিলিয়ান তরুণীকে। ফল? মোটা মাইনের ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয় তরুণীকে! নিজের অধিকারের সিটটি ছেড়ে না দেওয়া মানুষটির গায়ে অপরাধীর তকমা সেঁটে দেয় সোশ্যাল মিডিয়ার বিচারকরা। দিল্লি মেট্রোর ঘটনার থেকে এই ঘটনাটিকে তফাৎ করা যায় কি?
ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে আমরা ভয় পাই, নাক সিঁটকাই, অথবা হাসি। মনের সুখে ঠিক-ভুলের বিচার করতে বসি। তারপর অন্যদের দেখাই। তারপর দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝে কখন যেন ভুলে গিয়ে আবার ব্যক্তিগত জীবনযাপনের কাজে মন লাগাই। ভুলতে পারে না সেই ব্যক্তি, যাকে ‘ভাইরাল’ করে দেওয়া হয়েছে। সারাজীবন ক্ষতের দাগের মতো বয়ে বেড়াতে হয় তাকে। এর ফলে যেমন বহু ক্ষেত্রে সত্যিই আসল অপরাধীদের শাস্তি পাওয়ানো যায়, তেমনই ভুল বুঝে গোটা জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার নজিরও কম দেখতে মেলে না।
কোনও অস্ত্রের ক্ষেত্রেই বোধহয় অপব্যবহারের সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাই না? ব্যবহারকারীর ভূমিকাই নির্ধারণ করে দেয় যে সত্যি করেই ঠিক কতখানি রোগের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে অন্যকে ‘ভাইরাল’ করে দেওয়ার ইচ্ছে।