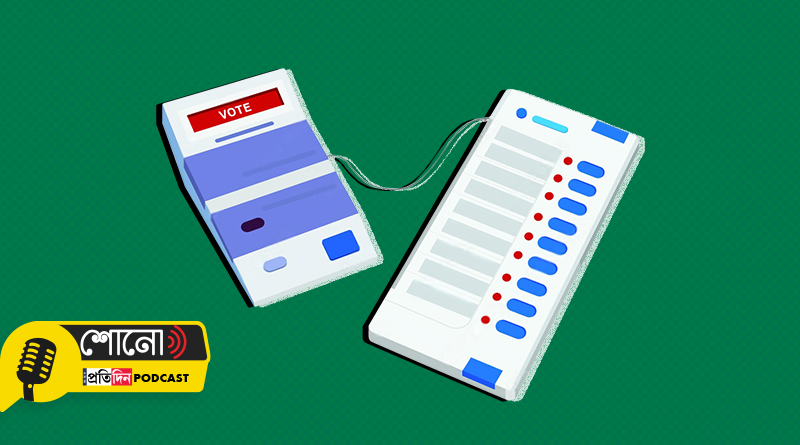অন্যের সৃষ্টি পছন্দ নয়, এমন হলে কেমন প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের?
- Published by: Saroj Darbar
- Posted on: July 21, 2024 7:13 pm
- Updated: July 21, 2024 7:13 pm


সময় নিজের মতো করে তার ফসল গুছিয়ে নেয়। ফলত কোনও মত বা ভাবনাই শাশ্বত কিংবা ঋত হয়তো নয়। তবে সময়ের মজা এই যে, এক-একসময় পুরনো প্রশ্ন ফিরে আসে নতুন অর্থ নিয়ে। যেমন আজকের সময়ে আবার নতুন করে প্রশ্ন করতে শিখছে, ‘আর্টের উদ্দেশ্য কি সংবাদ দেওয়া বা তর্ক করা?’ এ প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই।
যে কোনও সৃষ্টির প্রতি সমালোচনামুখর হওয়া দোষের কিছু নয়। বরং তা স্বাস্থ্যকর। তবে, কোন গুণে যে সমালোচনার জায়গাটিও আলাদা হয়ে যায়, তা খেয়াল করা জরুরি। এই বিশেষ গুণের অভাবেই ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যকে প্রমথ চৌধুরী ‘চোয়াড়ে’ বলে খানিক কম নম্বর দিয়েছিলেন। তুলনায় এগিয়ে রেখেছিলেন ইউরোপে ফরাসি গদ্যসাহিত্যের প্রসিদ্ধিকে। আসলে সমালোচনাও সামাজিক ভদ্রতা গুণের বাইরে নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকালেই সেই গুণটি চিহ্নিত করা যায়।
সমকালে নিজের লেখার সমালোচনা তো বটেই, কখনও তা নিয়ে এমনকী ব্যঙ্গও শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদল মানুষ ছিলেন যাঁদের নাকি কাজই ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষার ও ছন্দের খুঁত ধরা। এঁরা হলে তাঁরা, ‘রবীন্দ্রনাথ যাঁদের মুখে ভাষা দিয়েছেন এবং প্রাণে ছন্দ দিয়েছেন।’ রবীন্দ্রনাথ নিজেও ক্ষুরধার সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। কেউ যদি যুদ্ধ করার নেশাতেই রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানাতেন, তাহলে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি নন। তবে, সাধারণ ভাবে তাঁর সমালোচনার মধ্যে ওই সামাজিক গুণটি চিহ্নিত করা যেত, যা তাঁকে সমকালীন অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।
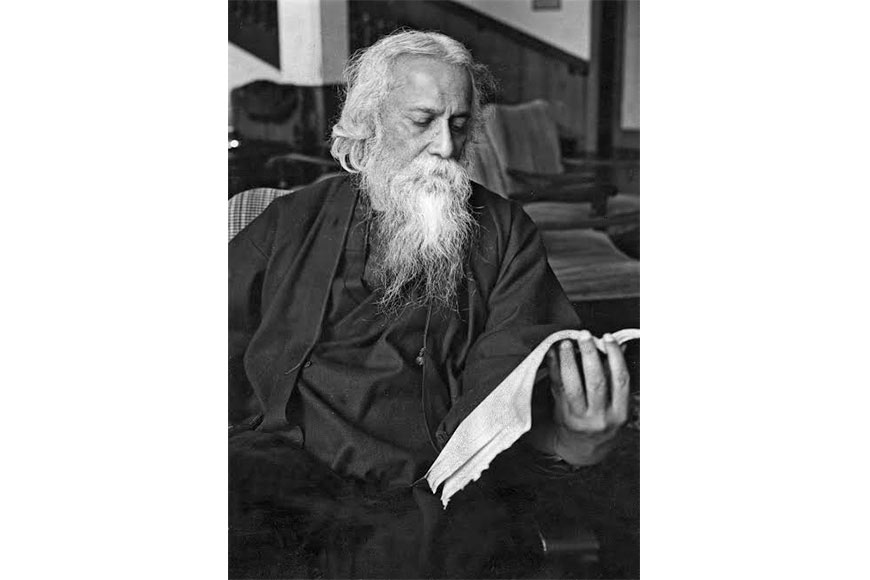
এমনকী কোনও বিষয়ে কথোপকথনের সময়, নিজের মত জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠাও যে তিনি সর্বদা করতে চেয়েছেন, তা নয়। যে গোঁড়ামি বা ডগমার বিপ্রতীপে তাঁর আজীবনের অবস্থান, সেই জায়গা থেকেই অন্যের কথা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন এবং প্রয়োজনে মান্যও করেছেন। এর হদিশও দিচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী, বলছেন, ‘আমি তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং মধ্যে মধ্যে তর্কও করেছি। আমার কথা যখন তাঁর মনঃপূত হয়েছে, তখন তিনি সে কথা গ্রাহ্য করতে তিল মাত্রও দ্বিধা করেননি। এটি আমার মতে একটা অসাধারণ গুণ। কারণ সাধারণ লোকে দেখতে পাই নিজের মত বজায় রাখবার জন্য বাকবিতণ্ডা অবলম্বন করে। এই কারণেই তর্ক জিনিসটা এত অসহ্য। কিন্তু তিনি যথার্থ সত্যদ্রষ্টা বলে অপরের চিন্তায় মান্য করতেন। আমাদের ক্ষুদ্র মনই ক্ষুদ্র অহং থেকে মুক্তি পায় না। আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন কখনও রবীন্দ্রনাথের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়নি।’
এই যে গ্রহণের ক্ষমতা, তা রবীন্দ্রনাথকে গুণগ্রাহী করে তুলেছিল অন্যের সৃষ্টি বিচারের ক্ষেত্রেও। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই সঞ্জীবচন্দ্রের ভ্রমণকাহিনির সৌন্দর্যের প্রতি তাই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিহারীলালের কাছে ঋণ স্বীকারেও তিনি মুক্তকণ্ঠ। শরৎকুমারীর ‘শুভবিবাহ’-এর সঙ্গে যেমন পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তেমনই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে হিউমারকে কবিতার পর্যায়ে ঊত্তীর্ণ করেছেন, তাও তিনি স্বীকার করেছেন কুণ্ঠাহীন ভাবে। দেখা গিয়েছে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সমকালীন লেখকদের সেভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, যতটা গুণগ্রাহী মনের পরিচয় দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তাঁর সমালোচনাতেও থাকছে এই সামাজিক ভদ্রতা গুণ। যা না থাকলে সাহিত্য বা সমালোচনা কোনোটাই প্রীতিকর হয় না।
অন্যের সৃষ্টি যে সবসময় তাঁর মনে ধরেছে তাও নয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও অন্যান্যদের আয়োজনে সেবার এক সাহিত্যসভায় গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে পড়া একটা গল্পও ভালো লাগল না তাঁর। পরে শিলাইদহ থেকে প্রশান্তচন্দ্রকে তিনি লিখলেন, ‘তোমাদের সভায় যে গল্প পড়া হয়েছিল সেটাকে আমি তো কোনমতেই আর্টের কোটায় ফেলতে পারিনে। আর্টের উদ্দেশ্য কি সংবাদ দেওয়া বা তর্ক করা?’ স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার সঙ্গে সেই সময়কার লেখালিখির ঠিক মিল হচ্ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই ভালো-না-লাগাকে অকারণ নিন্দেমন্দ বা তর্কের জায়গায় নিয়ে যাননি। বরং তিনি এই সূত্রটিকে সাহিত্য বা শিল্পের এক চিরকালীন প্রশ্নে তুলে আনলেন। শিল্পের উদ্দেশ্য কী? এই তাঁর কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। এবং তাঁর মত, ‘পৃথিবীতে অনেক রকমের মনোবিকার আছে অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যকে কি তারই মিউজিয়াম করতে হবে? … আমরা হাসপাতাল কিম্বা পাগলাগারদকেই তো সাহিত্যের বিষয় করতে পারিনে- অথচ রোগীকে ও পাগলকে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে একথা সত্য। স্বাস্থ্য ও প্রকৃতিস্থতাই হল গিয়ে সত্যের পূর্ণতা, সেই জন্যেই সেই পরিপূর্ণতার মধ্যে অস্বাস্থ্য ও পাগলামি অনায়াসে স্থান নিতে পারে- এর উলটো কাণ্ড করতে গেলে কখনোই সেটাতে আমাদের মন প্রসন্ন হতে পারে না।’
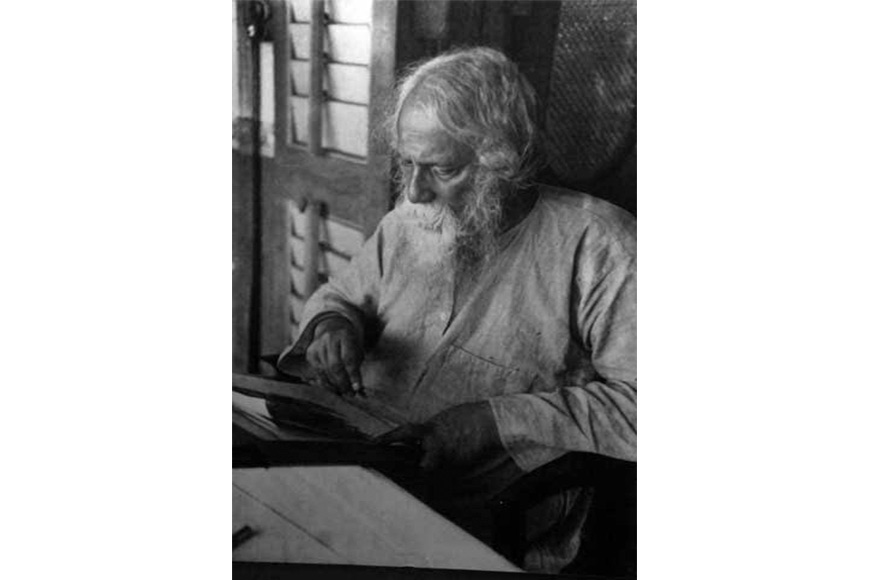
এখন, প্রসন্নতাই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কিনা, এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অতএব রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে-প্রশ্ন তুলে পক্ষে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘আধুনিক য়ুরোপে আর্ট সম্বন্ধে যে ঘোরতর পাগলামি দেখা দিয়েচে তাকে কি চূড়ান্ত বলেই মেনে নিতে হবে?… শুচিবায়ু বলে একটা বায়ু আছে সেটাকে ত্যাগ করা চাই, কিন্তু অশুচিবায়ু বলে যে বায়ু আছে সেটাকেই কি গ্রহণ করতে হবে? আমি তো রাজি না- তার হয়তো একটা কারণ যে আমার বয়স প্রায় বাষট্টি হল।’
বয়সের উল্লেখটি আলাদা করে মনে রাখার মতো। কেননা ওই বয়সে এসে তিনি যে পরিপূর্ণতার কথা ভাবছিলেন, তা হয়তো অন্যদের ভাবনায় পাচ্ছিলেন না। অথবা তিনি যে ভাবনায় থিতু, তা তাঁর আজীবনের একটা কেন্দ্রীয় ভাবনাই- সেই কথাটিই মনে করিয়ে দিতে চাইছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের এই মতেই যে বাংলা সাহিত্য চিরকাল আটকে থেকেছে তা নয়। থাকার কথাও নয়। তবে, ভালো-না-লাগা গল্পের সমালোচনা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক ভদ্রতা গুণ থেকে সরে যাচ্ছেন না। বরং একটি প্রতর্কেরই জন্ম দিচ্ছেন, যা চিরকালীন। সময়ে সময়েই তা ফিরে ফিরে আসে। সময় নিজের মতো করে তার ফসল গুছিয়ে নেয়। ফলত কোনও মত বা ভাবনাই শাশ্বত কিংবা ঋত হয়তো নয়। তবে সময়ের মজা এই যে, এক-একসময় পুরনো প্রশ্ন ফিরে আসে নতুন অর্থ নিয়ে। যেমন আজকের সময়ে আবার নতুন করে প্রশ্ন করতে শিখছে, ‘আর্টের উদ্দেশ্য কি সংবাদ দেওয়া বা তর্ক করা?’
এ প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই। বহুকাল আগে। তবে উত্তর খোঁজার দায় একান্ত সমসময়েরই।